আহা! স্মার্ট গ্যাজেটের জগৎ!
আহা! স্মার্ট গ্যাজেটের জগৎ!
জাহীদ রেজা নূর

ষোলো বছর বয়সী ছেলেটার গোমড়া মুখ। মাঝে মাঝে বারান্দায় চলে যাচ্ছে। ফিরে আসার পর মুখে পাওয়া যাচ্ছে সিগারেটের কড়া গন্ধ। ও সেটা বুঝতে পারছে না। মনে করছে, লুকিয়েই খাওয়া গেছে সিগারেটটা। গন্ধ-টন্ধ নেই ঠোঁটে।
ফেসবুকের মেসেঞ্জারে একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওর। যখন মনে হয়েছে, এই মেয়েটাকে ছাড়া বাঁচবে না, তখনই মেয়েটা নানা ধরনের টালবাহানা শুরু করেছে। সরে যেতে চাইছে। এত গভীর প্রেম; কিন্তু কোনোদিন দেখাই হয়নি তাদের। ভার্চুয়াল প্রেমেই শুরু হয়েছে টানাপোড়েন। ছেলেটা দু-একবার আত্মহত্যার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে বন্ধুদের কাছে। মা-বাবাকে বন্ধুরা সাবধানও করে গেছে। ওর দিকে খেয়াল রাখতে বলেছে।
ছেলেটা সিগারেটের পর গাঁজা, অ্যালকোহল ধরনের নেশায় আকৃষ্ট হয়েছে। সারা দিন ঘুরে বেড়ায় স্মার্টফোনে।
বাবা সরকারি কাজে ইউরোপের একটা বড় শহরে। মা-ও করেন বড় চাকরি। অর্থবিত্তের অভাব নেই কোনো। ইংরেজি মাধ্যমে পড়া মেয়েটির ভালোই থাকার কথা। কিন্তু একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল, মেয়েটি ভুগছে ডিপ্রেশনে। মা-বাবা সময় দেন না বলেই মনে বেড়ে উঠেছে অসুখ। কারও জন্যই সে প্রয়োজনীয় নয়–এই ভাবনা থেকে ও ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে বন্দী হয়ে যেতে থাকে। কারও সঙ্গে কথা বলে না। চিকিৎসকের পরামর্শে মা চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। চলে যান ইউরোপে, চিকিৎসা করান মেয়ের এবং সময় দেন মেয়েকে। মেয়েটা ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসতে শুরু করে নিজের জীবনে। সে সময় মেয়েকে সময় দিতে শুরু না করলে বিপদ ঘটে যেতে পারত।
আমরা জেনারেশন জেড বা জি (মার্কিন মুলুকে জেডকে জি বলা হয়) নিয়ে কথা বলছি। মোটামুটি ১৯৯৫ সালের পর জন্ম নেওয়া প্রজন্মকেই জেনারেশন জেড বা জি বলা হয়। এই এক প্রজন্ম, যাদের চিনে নিতে কষ্ট হয়, চিনে নিতে ভুল হয়। অভিভাবকেরা এত বড় চ্যালেঞ্জের মুখে আগে কখনো পড়েননি। জেড বা জি প্রজন্মের সন্তানেরাও অভিভাবকদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নিচ্ছে নিজের মতো করে। মূলত গ্যাজেট-দুনিয়াই পাল্টে দিয়েছে সম্পর্কগুলো।
মনে করার কোনো কারণ নেই, পৃথিবীতে সব সময়ই পূর্বপ্রজন্মের কাছে উত্তরপ্রজন্ম নতজানু হয়ে থেকেছে এবং পূর্বপ্রজন্ম যা বলেছে, লক্ষ্মী সন্তানের মতো তা পালন করেছে। বরং উল্টো। সব সময়ই নতুন প্রজন্ম বিদ্রোহ করতে চেয়েছে।
বলেছে, ‘তোমাদের শেখানো বিদ্যে এখন আর কার্যকরী নয়। জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাও।’ কিছুদিন পর নতুন-পুরোনো মিলে একটা তরতাজা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড়িয়ে গেছে। ওই থিসিস-অ্যান্টিথিসিস=সিনথেসিস। সংশ্লেষের এই সূত্রটি এখনো সত্য।
কিন্তু সেই পরিবর্তনগুলো ঘটেছে ধীরে ধীরে। রেনেসাঁ, শিল্পবিপ্লব সময়কে নাড়িয়ে দিয়েছিল ভীষণভাবে। দুই বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অবিশ্বাসের পথ বেয়ে পৃথিবীজুড়ে যে মানবদর্শন স্থিত হচ্ছিল, সেটাকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করেছে তথ্যপ্রযুক্তির গতিশীলতা। আর সে পথেই আমাদের নতুন জি বা জেড প্রজন্ম এগিয়ে চলেছে। তাদের এই পাল্টে যাওয়া জীবনকে বোঝা খুব দরকার। অকারণে দোষারোপ কোনো কাজে দেবে না।
শিশুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে বলতে পারবেন মনোবিদেরাই। আমরা শুধু জীবনযাপনে গ্যাজেট ব্যবহারের স্বাভাবিক প্রবণতা আর তাতে লাভক্ষতির হিসাব-নিকাশটা একটু উসকে দেব। করোনার এই ভয়াবহ সময়টায় ঘরে আটকে থাকতে থাকতে আমাদের সন্তানেরাও যে মানসিক ও শারীরিকভাবে ভালো নেই, সে সত্যটি উপলব্ধি করতে অনুরোধ করব সবাইকে।
সবার আগে দেখা যাক, এই নতুন সময়টায় শিশুরা কোন জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ওদের হাতে স্মার্টফোন আছে। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জেও স্মার্টফোন চলে এসেছে। তবে এখনো অনেক ক্ষেত্রে তা শিশুদের নাগালের বাইরে। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে ১০ বছরের শিশুও এখন স্মার্টফোনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। আমাদের শহরাঞ্চলের অবস্থাও অনেকটা সে রকম।
ই-বুক, নোটবুক, ট্যাব, মিউজিক্যাল সেন্টার প্রভৃতি এখন তাদের হাতের কাছেই। এগুলো প্রথমে মানুষের সেবায় লাগে। এরপর মানুষই এদের সেবা করতে শুরু করে। অর্থাৎ এদের ছাড়া আর চলতে পারে না। যখন গ্যাজেটের ওপর নির্ভরতা বাড়তে থাকে, তখন সত্যিই অভ্যস্ত পথ ভুলে এক অজানা পথ পাড়ি দিতে হয়, যা সব সময় আনন্দময় হয় না।
গবেষকেরা কিন্তু বসে নেই। স্কুল, কলেজপড়ুয়া শিশু ও তরুণদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে তাঁরা দেখেছেন, এরা ৮ থেকে ২৪ ঘণ্টা (!) ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সান্নিধ্যে থাকে। এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। বিষণ্ণতা, মন খারাপ, বিভ্রান্তি, হতাশা, যেকোনো ছোটখাটো বিষয়ে রাগ করা ইত্যাদি তাদের সঙ্গী হয়ে যায়।
অভিভাবকেরা এ সময় কী করছেন? তাঁরা শিশুদের ছেড়ে দিচ্ছেন ভার্চুয়াল জগতে। সেখানে ভাবতে হয় না কিছু। ভেবে দেয় যন্ত্র। বিদ্যা, সৃজনশীলতার প্রতি আগ্রহ না থাকলেও চলে। কারণ, হাতের মুঠোয় যে জগৎটা আছে, তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভুলিয়ে দেয়। একটি ছোট্ট গ্যাজেটের মধ্যেই থাকে গোটা দুনিয়া। আশপাশ নিয়ে কোনো আগ্রহ আর জাগে না মনে। মা-বাবা অথবা অন্য অভিভাবকদের সান্নিধ্যে থাকলে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। শিশুরা তাদের মনোজগতে জায়গা করে দিতে পারে বৈচিত্র্যময় নানা অভিজ্ঞতাকে। কিন্তু ভয়াবহ একটা বাস্তবতা ক্রমশ কাছিয়ে আসতে থাকে, যখন মা-বাবার জায়গাটাও দখল করে নেয় স্মার্টফোন, গুগল।
বড়দের কাজে নাক গলাচ্ছে না, নিজের স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ নিয়েই ব্যস্ত আছে সন্তান–এই আনন্দেই অনেকে সন্তানের হাতে তুলে দেন গ্যাজেট। তাতে সন্তানটির অগ্রাধিকারের জায়গা যায় বদলে। সে অগ্রাধিকার দেয় ভার্চুয়াল জগৎকে। এরপর বাস্তব জগৎ।
আসুন, কল্পনার রাজ্য থেকে একটু ঘুরে আসি। ঘাবড়াবেন না। আড়ালে বলে রাখি, এ নিছক কল্পনা নয়, স্মার্টফোন বা অন্য কোনো গ্যাজেটের ওপর শিশুদের নির্ভরতা নিয়ে চলা গবেষণা থেকেই তথ্যগুলো পাওয়া গেছে। শিশুটিকে প্রশ্ন করা হলো এবং বলা হলো, উত্তরে শুধু ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ বলতে।
প্রশ্নগুলো এ রকম:
- কম্পিউটার, স্মার্টফোন বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া আমার দিন কাটে না।
- গ্যাজেট ব্যবহার না করলে আমি নার্ভাস হয়ে যাই।
- ঠিক করি, অল্প সময়ের জন্য বসব স্মার্টফোন হাতে; কিন্তু সময় যে কখন পার হয়ে যায়, টেরই পাই না।
- কতটা সময় গ্যাজেট নিয়ে থাকি, সে কথা মা-বাবাকে বলি না। তাঁদের কাছে মিথ্যে বলি।
- শুধু স্মার্টফোন নিয়ে একাকী সময় কাটাতে চাই। আর কিছু চাই না।
- গ্যাজেট ব্যবহারের সময় অন্য সব জরুরি কাজের কথা ভুলে যাই।
- কম্পিউটার বা স্মার্টফোন ব্যবহার করার সময় আমার মেজাজ ফুরফুরে হয়ে যায়।
- মা-বাবাকে গেমের নতুন ভার্সন কিনে দিতে বাধ্য করি।
- গ্যাজেট ব্যবহারের পরে কখনো মাথা ধরে, চোখ কড়কড় করে, ঠিকভাবে ঘুম হয় না।
- বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে কম্পিউটার বা স্মার্টফোনে সময় কাটাতে ভালো লাগে।
এই ১০টি প্রশ্নের প্রতিটি ‘হ্যাঁ’-র জন্য যদি ১ নম্বর দেন, তাহলে ফলাফল কী হবে–তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন গবেষকেরা। তাঁরা বলছেন, যদি হ্যাঁ-র সংখ্যা ১ থেকে ৪-এর মধ্যে থাকে, তাহলে ভাববার কিছু নেই। যদি তা ৫ থেকে ৬-এর মধ্যে থাকে, তাহলে বোঝা যায়, গ্যাজেটের দিকে ঝুঁকছে শিশু, আর যদি তা ৭ থেকে ১০-এর মধ্যে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, গ্যাজেট তাকে আস্ত হজম করে নিয়েছে।
নিরাময় নিয়ে কথা বলার আমি কেউ নই। শিশুদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে কি এই গ্যাজেটনির্ভরতার ভয়াবহতা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে? সে কি বুঝবে? সচেতনভাবে কি ঠিক করে দেওয়া যায়, কতটা সময় গ্যাজেট হবে সঙ্গী, আর কতটা সময় বাইরের জগৎকে কাছে টেনে নিতে হবে? কেউ কেউ বলে থাকেন, সপ্তাহে এক বা দুই দিন একেবারেই গ্যাজেটের ধারেকাছে না যেতে, তাতে স্বাভাবিক জীবনের প্রতি আগ্রহ বাড়তে পারে। ভ্রমণে গেলে গ্যাজেট যেন সঙ্গী না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে পারলে ভালো।
এই যে বড় বড় কথা বলছি, বা কী করণীয়–এ রকম পরামর্শ দিচ্ছি, তাতে কি কারও কিছু আসে-যায়? আসলে শিশুটিকে গ্যাজেটের হাতে ছেড়ে দেওয়ার আগে অভিভাবকেরা তো ওর কাছ থেকে কী কী প্রত্যাশা করেন, তা-ও অবচেতনে ঠিক করে নিয়েছেন। ওর মনোজগৎ গোল্লায় যাক, ওর জিপিএ-ফাইভ যেন থাকে, তাহলেই হবে। আর প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিয়ে তা ‘মজাসে’ উপভোগ করার সময় অভিভাবকেরা ভেবেও দেখেন না, কতটা চাপ দিচ্ছেন ছোট্ট শিশুটির ছোট্ট বুকটায়!
এ রকম যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত করার দায়টা শিশুর না অভিভাবকের–সে প্রশ্নটা থাকল এখানে।
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা

ষোলো বছর বয়সী ছেলেটার গোমড়া মুখ। মাঝে মাঝে বারান্দায় চলে যাচ্ছে। ফিরে আসার পর মুখে পাওয়া যাচ্ছে সিগারেটের কড়া গন্ধ। ও সেটা বুঝতে পারছে না। মনে করছে, লুকিয়েই খাওয়া গেছে সিগারেটটা। গন্ধ-টন্ধ নেই ঠোঁটে।
ফেসবুকের মেসেঞ্জারে একটা মেয়ের সঙ্গে পরিচয় হয়েছে ওর। যখন মনে হয়েছে, এই মেয়েটাকে ছাড়া বাঁচবে না, তখনই মেয়েটা নানা ধরনের টালবাহানা শুরু করেছে। সরে যেতে চাইছে। এত গভীর প্রেম; কিন্তু কোনোদিন দেখাই হয়নি তাদের। ভার্চুয়াল প্রেমেই শুরু হয়েছে টানাপোড়েন। ছেলেটা দু-একবার আত্মহত্যার ইঙ্গিত দিয়ে রেখেছে বন্ধুদের কাছে। মা-বাবাকে বন্ধুরা সাবধানও করে গেছে। ওর দিকে খেয়াল রাখতে বলেছে।
ছেলেটা সিগারেটের পর গাঁজা, অ্যালকোহল ধরনের নেশায় আকৃষ্ট হয়েছে। সারা দিন ঘুরে বেড়ায় স্মার্টফোনে।
বাবা সরকারি কাজে ইউরোপের একটা বড় শহরে। মা-ও করেন বড় চাকরি। অর্থবিত্তের অভাব নেই কোনো। ইংরেজি মাধ্যমে পড়া মেয়েটির ভালোই থাকার কথা। কিন্তু একদিন হঠাৎ আবিষ্কার করা গেল, মেয়েটি ভুগছে ডিপ্রেশনে। মা-বাবা সময় দেন না বলেই মনে বেড়ে উঠেছে অসুখ। কারও জন্যই সে প্রয়োজনীয় নয়–এই ভাবনা থেকে ও ধীরে ধীরে নিজের মধ্যে বন্দী হয়ে যেতে থাকে। কারও সঙ্গে কথা বলে না। চিকিৎসকের পরামর্শে মা চাকরি ছেড়ে দিতে বাধ্য হন। চলে যান ইউরোপে, চিকিৎসা করান মেয়ের এবং সময় দেন মেয়েকে। মেয়েটা ধীরে ধীরে আবার ফিরে আসতে শুরু করে নিজের জীবনে। সে সময় মেয়েকে সময় দিতে শুরু না করলে বিপদ ঘটে যেতে পারত।
আমরা জেনারেশন জেড বা জি (মার্কিন মুলুকে জেডকে জি বলা হয়) নিয়ে কথা বলছি। মোটামুটি ১৯৯৫ সালের পর জন্ম নেওয়া প্রজন্মকেই জেনারেশন জেড বা জি বলা হয়। এই এক প্রজন্ম, যাদের চিনে নিতে কষ্ট হয়, চিনে নিতে ভুল হয়। অভিভাবকেরা এত বড় চ্যালেঞ্জের মুখে আগে কখনো পড়েননি। জেড বা জি প্রজন্মের সন্তানেরাও অভিভাবকদের সঙ্গে সম্পর্ক গড়ে নিচ্ছে নিজের মতো করে। মূলত গ্যাজেট-দুনিয়াই পাল্টে দিয়েছে সম্পর্কগুলো।
মনে করার কোনো কারণ নেই, পৃথিবীতে সব সময়ই পূর্বপ্রজন্মের কাছে উত্তরপ্রজন্ম নতজানু হয়ে থেকেছে এবং পূর্বপ্রজন্ম যা বলেছে, লক্ষ্মী সন্তানের মতো তা পালন করেছে। বরং উল্টো। সব সময়ই নতুন প্রজন্ম বিদ্রোহ করতে চেয়েছে।
বলেছে, ‘তোমাদের শেখানো বিদ্যে এখন আর কার্যকরী নয়। জীবনকে দেখার দৃষ্টিভঙ্গি বদলাও।’ কিছুদিন পর নতুন-পুরোনো মিলে একটা তরতাজা নতুন দৃষ্টিভঙ্গি দাঁড়িয়ে গেছে। ওই থিসিস-অ্যান্টিথিসিস=সিনথেসিস। সংশ্লেষের এই সূত্রটি এখনো সত্য।
কিন্তু সেই পরিবর্তনগুলো ঘটেছে ধীরে ধীরে। রেনেসাঁ, শিল্পবিপ্লব সময়কে নাড়িয়ে দিয়েছিল ভীষণভাবে। দুই বিশ্বযুদ্ধ-পরবর্তী অবিশ্বাসের পথ বেয়ে পৃথিবীজুড়ে যে মানবদর্শন স্থিত হচ্ছিল, সেটাকে প্রচণ্ড বেগে আঘাত করেছে তথ্যপ্রযুক্তির গতিশীলতা। আর সে পথেই আমাদের নতুন জি বা জেড প্রজন্ম এগিয়ে চলেছে। তাদের এই পাল্টে যাওয়া জীবনকে বোঝা খুব দরকার। অকারণে দোষারোপ কোনো কাজে দেবে না।
শিশুদের মনস্তত্ত্ব নিয়ে বলতে পারবেন মনোবিদেরাই। আমরা শুধু জীবনযাপনে গ্যাজেট ব্যবহারের স্বাভাবিক প্রবণতা আর তাতে লাভক্ষতির হিসাব-নিকাশটা একটু উসকে দেব। করোনার এই ভয়াবহ সময়টায় ঘরে আটকে থাকতে থাকতে আমাদের সন্তানেরাও যে মানসিক ও শারীরিকভাবে ভালো নেই, সে সত্যটি উপলব্ধি করতে অনুরোধ করব সবাইকে।
সবার আগে দেখা যাক, এই নতুন সময়টায় শিশুরা কোন জীবনযাপন পদ্ধতির মধ্য দিয়ে যাচ্ছে। ওদের হাতে স্মার্টফোন আছে। বাংলাদেশের গ্রামগঞ্জেও স্মার্টফোন চলে এসেছে। তবে এখনো অনেক ক্ষেত্রে তা শিশুদের নাগালের বাইরে। কিন্তু পশ্চিমা বিশ্বে ১০ বছরের শিশুও এখন স্মার্টফোনে অভ্যস্ত হয়ে উঠছে। আমাদের শহরাঞ্চলের অবস্থাও অনেকটা সে রকম।
ই-বুক, নোটবুক, ট্যাব, মিউজিক্যাল সেন্টার প্রভৃতি এখন তাদের হাতের কাছেই। এগুলো প্রথমে মানুষের সেবায় লাগে। এরপর মানুষই এদের সেবা করতে শুরু করে। অর্থাৎ এদের ছাড়া আর চলতে পারে না। যখন গ্যাজেটের ওপর নির্ভরতা বাড়তে থাকে, তখন সত্যিই অভ্যস্ত পথ ভুলে এক অজানা পথ পাড়ি দিতে হয়, যা সব সময় আনন্দময় হয় না।
গবেষকেরা কিন্তু বসে নেই। স্কুল, কলেজপড়ুয়া শিশু ও তরুণদের মধ্যে জরিপ চালিয়ে তাঁরা দেখেছেন, এরা ৮ থেকে ২৪ ঘণ্টা (!) ইলেকট্রিক বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতির সান্নিধ্যে থাকে। এর কিছু পার্শ্বপ্রতিক্রিয়াও দেখা যায়। বিষণ্ণতা, মন খারাপ, বিভ্রান্তি, হতাশা, যেকোনো ছোটখাটো বিষয়ে রাগ করা ইত্যাদি তাদের সঙ্গী হয়ে যায়।
অভিভাবকেরা এ সময় কী করছেন? তাঁরা শিশুদের ছেড়ে দিচ্ছেন ভার্চুয়াল জগতে। সেখানে ভাবতে হয় না কিছু। ভেবে দেয় যন্ত্র। বিদ্যা, সৃজনশীলতার প্রতি আগ্রহ না থাকলেও চলে। কারণ, হাতের মুঠোয় যে জগৎটা আছে, তা বিশ্বব্রহ্মাণ্ডকে ভুলিয়ে দেয়। একটি ছোট্ট গ্যাজেটের মধ্যেই থাকে গোটা দুনিয়া। আশপাশ নিয়ে কোনো আগ্রহ আর জাগে না মনে। মা-বাবা অথবা অন্য অভিভাবকদের সান্নিধ্যে থাকলে নানা বিষয়ে আলোচনা হয়। শিশুরা তাদের মনোজগতে জায়গা করে দিতে পারে বৈচিত্র্যময় নানা অভিজ্ঞতাকে। কিন্তু ভয়াবহ একটা বাস্তবতা ক্রমশ কাছিয়ে আসতে থাকে, যখন মা-বাবার জায়গাটাও দখল করে নেয় স্মার্টফোন, গুগল।
বড়দের কাজে নাক গলাচ্ছে না, নিজের স্মার্টফোন বা ল্যাপটপ নিয়েই ব্যস্ত আছে সন্তান–এই আনন্দেই অনেকে সন্তানের হাতে তুলে দেন গ্যাজেট। তাতে সন্তানটির অগ্রাধিকারের জায়গা যায় বদলে। সে অগ্রাধিকার দেয় ভার্চুয়াল জগৎকে। এরপর বাস্তব জগৎ।
আসুন, কল্পনার রাজ্য থেকে একটু ঘুরে আসি। ঘাবড়াবেন না। আড়ালে বলে রাখি, এ নিছক কল্পনা নয়, স্মার্টফোন বা অন্য কোনো গ্যাজেটের ওপর শিশুদের নির্ভরতা নিয়ে চলা গবেষণা থেকেই তথ্যগুলো পাওয়া গেছে। শিশুটিকে প্রশ্ন করা হলো এবং বলা হলো, উত্তরে শুধু ‘হ্যাঁ’ বা ‘না’ বলতে।
প্রশ্নগুলো এ রকম:
- কম্পিউটার, স্মার্টফোন বা ইলেকট্রনিক যন্ত্রপাতি ছাড়া আমার দিন কাটে না।
- গ্যাজেট ব্যবহার না করলে আমি নার্ভাস হয়ে যাই।
- ঠিক করি, অল্প সময়ের জন্য বসব স্মার্টফোন হাতে; কিন্তু সময় যে কখন পার হয়ে যায়, টেরই পাই না।
- কতটা সময় গ্যাজেট নিয়ে থাকি, সে কথা মা-বাবাকে বলি না। তাঁদের কাছে মিথ্যে বলি।
- শুধু স্মার্টফোন নিয়ে একাকী সময় কাটাতে চাই। আর কিছু চাই না।
- গ্যাজেট ব্যবহারের সময় অন্য সব জরুরি কাজের কথা ভুলে যাই।
- কম্পিউটার বা স্মার্টফোন ব্যবহার করার সময় আমার মেজাজ ফুরফুরে হয়ে যায়।
- মা-বাবাকে গেমের নতুন ভার্সন কিনে দিতে বাধ্য করি।
- গ্যাজেট ব্যবহারের পরে কখনো মাথা ধরে, চোখ কড়কড় করে, ঠিকভাবে ঘুম হয় না।
- বন্ধুদের সঙ্গে ঘুরে বেড়ানোর চেয়ে কম্পিউটার বা স্মার্টফোনে সময় কাটাতে ভালো লাগে।
এই ১০টি প্রশ্নের প্রতিটি ‘হ্যাঁ’-র জন্য যদি ১ নম্বর দেন, তাহলে ফলাফল কী হবে–তা নিয়ে মাথা ঘামিয়েছেন গবেষকেরা। তাঁরা বলছেন, যদি হ্যাঁ-র সংখ্যা ১ থেকে ৪-এর মধ্যে থাকে, তাহলে ভাববার কিছু নেই। যদি তা ৫ থেকে ৬-এর মধ্যে থাকে, তাহলে বোঝা যায়, গ্যাজেটের দিকে ঝুঁকছে শিশু, আর যদি তা ৭ থেকে ১০-এর মধ্যে থাকে, তাহলে বুঝতে হবে, গ্যাজেট তাকে আস্ত হজম করে নিয়েছে।
নিরাময় নিয়ে কথা বলার আমি কেউ নই। শিশুদের সঙ্গে কথোপকথনের মাধ্যমে কি এই গ্যাজেটনির্ভরতার ভয়াবহতা থেকে রেহাই পাওয়া যাবে? সে কি বুঝবে? সচেতনভাবে কি ঠিক করে দেওয়া যায়, কতটা সময় গ্যাজেট হবে সঙ্গী, আর কতটা সময় বাইরের জগৎকে কাছে টেনে নিতে হবে? কেউ কেউ বলে থাকেন, সপ্তাহে এক বা দুই দিন একেবারেই গ্যাজেটের ধারেকাছে না যেতে, তাতে স্বাভাবিক জীবনের প্রতি আগ্রহ বাড়তে পারে। ভ্রমণে গেলে গ্যাজেট যেন সঙ্গী না হয়, সেটা নিশ্চিত করতে পারলে ভালো।
এই যে বড় বড় কথা বলছি, বা কী করণীয়–এ রকম পরামর্শ দিচ্ছি, তাতে কি কারও কিছু আসে-যায়? আসলে শিশুটিকে গ্যাজেটের হাতে ছেড়ে দেওয়ার আগে অভিভাবকেরা তো ওর কাছ থেকে কী কী প্রত্যাশা করেন, তা-ও অবচেতনে ঠিক করে নিয়েছেন। ওর মনোজগৎ গোল্লায় যাক, ওর জিপিএ-ফাইভ যেন থাকে, তাহলেই হবে। আর প্রতিযোগিতায় নামিয়ে দিয়ে তা ‘মজাসে’ উপভোগ করার সময় অভিভাবকেরা ভেবেও দেখেন না, কতটা চাপ দিচ্ছেন ছোট্ট শিশুটির ছোট্ট বুকটায়!
এ রকম যান্ত্রিক জীবনে অভ্যস্ত করার দায়টা শিশুর না অভিভাবকের–সে প্রশ্নটা থাকল এখানে।
লেখক: উপসম্পাদক, আজকের পত্রিকা
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
সম্পর্কিত

গরিবের ভরসা শুধুই উপরওয়ালা
এখন রাজনীতির এক গতিময়তার সময়। শেখ হাসিনার ১৫ বছরের গণতন্ত্রহীন কর্তৃত্ববাদী দুর্নীতিপরায়ণ শাসন ছাত্র আন্দোলনে উচ্ছেদ হয়ে যাওয়ার পর অন্তর্বর্তী শাসনকালে দ্রুততার সঙ্গে নানা রকম রাজনৈতিক কথাবার্তা, চিন্তা-ভাবনা, চেষ্টা-অপচেষ্টা, ক্রিয়া-প্রতিক্রিয়ার প্রকাশ ঘটছে।
২ ঘণ্টা আগে
ভাতের অধিকার ও গণতন্ত্র
বহু বছর আগে সেই ব্রিটিশ যুগে কাজী নজরুল লিখেছিলেন, ‘ক্ষুধাতুর শিশু চায় না স্বরাজ, চায় দুটো ভাত, একটু নুন।’ আসলে পেটের খিদে নিয়ম, আইন, বিবেক, বিচার কোনো কিছুই মানে না। তাই তো প্রবাদ সৃষ্টি হয়েছে, খিদের জ্বালা বড় জ্বালা। এর থেকে বোধ হয় আর কোনো অসহায়তা নেই। খালি পেটে কেউ তত্ত্ব শুনতে চায় না। কাওয়ালিও ন
২ ঘণ্টা আগে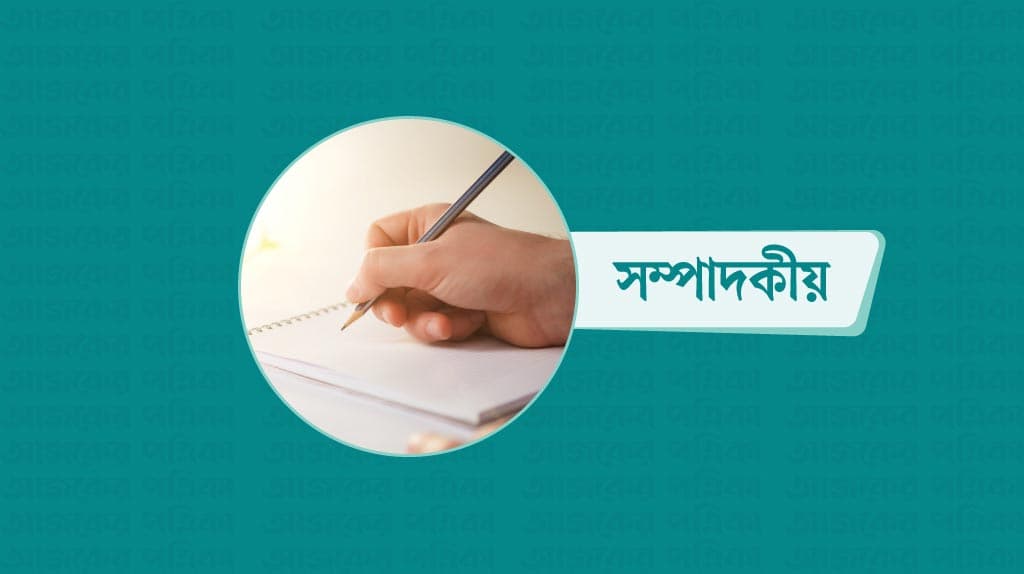
বাবার নৃশংসতা
তিন বছরের শিশু মুসা মোল্লা ও সাত বছরের রোহান মোল্লা নিষ্পাপ, ফুলের মতো কোমল। কারও সঙ্গে তাদের কোনো স্বার্থের দ্বন্দ্ব থাকার কথা নয়। কিন্তু বাবার চরম নিষ্ঠুরতায় পৃথিবী ছাড়তে হয়েছে তাদের। আহাদ মোল্লা নামের এক ব্যক্তি দুই ছেলেসন্তানকে গলা কেটে হত্যা করার পর নিজের গলায় নিজে ছুরি চালিয়েছেন।
২ ঘণ্টা আগে
নজিরবিহীন বাস্তবতায় একটি সরকার
দলীয় রাজনৈতিক সরকারের সঙ্গে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের তুলনা হতে পারে কি না, সেই প্রশ্ন পাশে রেখেই ইউনূস সরকারের কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে এর ১০০ দিন পেরিয়ে যাওয়ার সময়টায়। তবে সাধারণ মানুষ মনে হয় প্রতিদিনই তার জীবনে সরকারের ভূমিকা বিচার করে দেখছে।
১ দিন আগে



