নির্বাসনের দিনগুলি
নির্বাসনের দিনগুলি
শেখ ফজলে শামস পরশ

খুব ভোরে প্রচণ্ড ভাঙচুরের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙে। উঠে দেখি মা নেই পাশে। বিছানায় শুধু আমরা দুই ভাই। জানালা দিয়ে ঝড়ের মতো গোলাগুলি হচ্ছে। গুলিগুলো দেয়াল ফুটো করে মেঝেতে আছড়ে পড়ছে। সিঁড়িঘরে অনেক কান্নাকাটির আওয়াজ, হইচই। আমরা দুই ভাই ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়িঘরের দিকে গিয়ে দেখি বাবা-মা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়া। মায়ের পা দুটো বাবার বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা। দাদির শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোপুটি যাচ্ছে, আর দাদি পাগলের মতো প্রলাপ বকছেন, দেয়ালে কপাল ঠুকছেন।
এ অবস্থায় উনি আমার বড় চাচিকে বললেন, ‘ফাতু (শেখ সেলিম কাকার সহধর্মিণী ফাতেমা চাচি), আরজুর পা দুটি মণির বুকের ওপর থেকে সরাও।’
সেলিম কাকা (শেখ সেলিম কাকা) আর চাচি বাবা-মার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে মাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করছেন। আর বাবা পুরোপুরি নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছেন। মুখে কোনো কষ্টের চিহ্ন নাই। মনে হচ্ছে উনি যেন শান্তির নিদ্রায় বিভোর। শুধু গলায় কণ্ঠমণির নিচে চামড়া উঠে যাওয়ার একটা চিহ্ন। বাবার শরীরের অন্য কোথাও কোনো ক্ষত আমার মনে নাই। আমরা দুই ভাই কান্নাকাটি করছিলাম। মনে হয় আমরা ভয়েই কাঁদছিলাম; কারণ, মৃত্যু কাকে বলে তখনো আমরা জানি না। মৃত্যুর পর যে মানুষকে আর পাওয়া যায় না, সেটাও আমার জানা ছিল না। মৃত্যুর সাথে ওই আমার প্রথম পরিচয়। একসাথে অনেকগুলো মৃত্যু।
মায়ের মনে হয় অনেক কষ্ট হচ্ছিল আমাদের ফেলে যেতে। মা পানি খেতে চাচ্ছিলেন এবং বেঁচে থাকার চেষ্টা করছিলেন। বাইরে তখনো গুলির আওয়াজ থামে নাই। ভয়ানক গোলাগুলির আওয়াজ আর তার সঙ্গে জানালা ভাঙচুরের আওয়াজ।
মা চাচিকে বললেন, ‘ফাতু আমাকে বাঁচাও। আমার পরশ-তাপস! ওদেরকে তুমি দেইখো।’
ওটাই বোধ হয় মায়ের শেষ কথা। এর পর কী হলো আমি জানি না। গুলির আওয়াজ অনেক বেড়ে যাচ্ছিল এবং কারা যেন এদিকে আবার আসছিল। আমার চাচি তখন আমাদের নিয়ে তাঁর ড্রেসিংরুমে পালালেন। আমাদের মেঝেতে শুইয়ে রেখেছিলেন, যাতে গুলি না লাগে। গুলি মনে হয় বাথরুমের জানালা দিয়ে ড্রেসিংরুমেও ঢুকে যাচ্ছিল।
এর পর আর বাবা-মার সঙ্গে আমাদের আর দেখা হয় নাই। শুনেছি সেলিম কাকা একটা গাড়িতে করে মাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর মারুফ কাকা অন্য এক গাড়িতে বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।
এর পর সবকিছু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর আমরা দুই ভাই, চাচি, দাদি, আর রেখা ফুফু এক কাপড়ে আমাদের বাসা থেকে বের হয়ে যাই। তখনো বুঝি নাই যে, ওটাই নিজেদের বাসা থেকে আমাদের শেষ প্রস্থান। আর কখনো ওই বাসায় ফিরতে পারব না। আমার বয়স তখন পাঁচ বছর, আর আমার ভাই তাপসের বয়স চার বছর। আমাদের বাসাটা ছিল ধানমন্ডি ১৩ নম্বর রোডে একটা কানাগলির রাস্তায়। বাসা থেকে বের হয়ে পাশেই ছিল এক বিদেশি রাষ্ট্রদূত ভবন। আমরা সেখানেই আশ্রয় নিই। ওখান থেকে আমরা দেখতে পাই, আমাদের বাসায় আর্মিদের আনাগোনা, লুটতরাজ। এর পর শুরু হয় আমাদের ভবঘুরে জীবনযাপন; একেক দিন একেক বাসায়।
কোনো বাসায় দুদিন, কোনো বাসায় চার দিন। আশ্রয়ার্থী হিসেবে এভাবেই চলতে থাকে বেশ কয়েক মাস। আমার কোনো ধারণা ছিল না, কেন আমরা নিজের বাসায় ফেরত যেতে পারছি না। পরে দাদি-চাচিদের মাধ্যমে বুঝলাম যে আর্মিরা আমাদের খুঁজছিল। কয়েকটি বাসায় আর্মিরা আমাদের খুঁজতেও এসেছিল। ভাগ্যিস আমরা সময়মতো সেই বাসা থেকে পালিয়ে অন্য বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলাম।
মাহুতটুলিতে মঞ্জু খালার বাসায় আমরা মনে হয় বেশ কিছুদিন ছিলাম। মঞ্জু খালা আমাদের পেয়ে অস্থির! আদর-যত্নেই ছিলাম। কিন্তু নিরাপত্তার অভাবে সে বাসায়ও শান্তিতে থাকতে পারিনি। চলে আসার সময় গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মঞ্জু খালা ভীষণ কেঁদেছিলেন। তখনো জানতাম না ওই কান্নার আড়ালের অন্তর্নিহিত কারণ।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মঞ্জু খালাও ১৫ আগস্ট তাঁর বাবা (আবদুর রব সেরনিয়াবাত), দুই বোন (আমার মা ও বেবি খালা), ভাই (আরিফ মামা) ও চার বছরের ভাতিজাকে (সুকান্ত বাবু) হারিয়েছেন। তারপর আবার আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাওয়াই তো ওনাদের জন্য প্রচণ্ড মানসিক চাপ ছিল।
আমার চাচির আব্বা, মরহুম সুলতান আহমেদ চৌধুরীর (শেখ সেলিম কাকার শ্বশুর) বাসায়ও আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেই বাসায় আর্মিরা রেইডও করেছিল। চাচির বড়বোন, আনু খালার পাঁচ বছর বয়সী সন্তান লিমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেছিল।
পরে অনেক কসরত করে এবং ধস্তাধস্তি করে লিমাকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয় ওর বাবা আজাদ আংকেল। চাচির মেজো ভাই, বাচ্চু মামাকেও আর্মিরা তুলে নিয়ে যায়। বাচ্চু মামা, সেলিম কাকা, মারুফ কাকাদের সীমানা পার করে দিয়ে আসার পরই তাঁকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যান কর্নেল শাহরিয়ার। আর তাঁকে পাওয়া যায়নি। এমনকি তাঁর লাশটাও ওরা ফেরত দেয়নি।
সবাই তখন সারাক্ষণ শুধু কাঁদত। কারও সন্তান হারানোর ব্যথা, কারও ভাইবোন হারানোর কষ্ট, আর আমাদের বাবা-মা হারানোর অন্তহীন কান্না। তবে কেউ কারও সামনে কাঁদতে পারত না। আড়ালে গিয়ে বোবা কান্না কাঁদত। আমাদের সামনে সবাই কান্না আড়াল করে ফেলত। কারণ, তখনো আমদের বলা হয়নি যে, আমাদের বাবা-মা আর নেই। এভাবেই জীবননাশের হুমকি আর ভয়ভীতিকে সঙ্গী করে আমাদের শোকাহত পরিবারের জীবনের গাড়ি চলতে থাকে।
সেলিম কাকা আর মারুফ কাকার জীবনে তখন চরম ঝুঁকি। মারুফ কাকা তখন খুনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীতে যোগ দিতে মেঘালয় চলে যান। সেলিম কাকাকে তো গুলিই করা হয়েছিল। অল্পের জন্য অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে যান। শুনেছি খুনিরা যখন বাবাকে মারতে আসে, চাচি সেলিম কাকাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে খবর দেন। সেলিম কাকা হুড়মুড় করে গিয়ে দেখে ওরা বন্দুক তাক করে আছে বাবার দিকে। সেলিম কাকা ওদের ধাক্কা দিলে ওরাও তাকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িঘরের কোনায় ফেলে দেয়।
ঠিক তখনই ওরা গুলি শুরু করে। রুমের কোনায় এবং নিচে পড়েছিলেন বলে হয়তো–বা গুলি তাঁর গায়ে লাগেনি। ওই মুহূর্তে মা তখন রুম থেকে বের হয়ে এসে বাবার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ান। আমার মা মনে হয় বাবাকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তাই প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই মা বাবার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেই মুহূর্তে তিনি আমাদের কথাও ভাবেননি। মা স্বামীর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার উদাহরণ রেখে গেছেন। হয়তো গুলি লাগার পর তাঁর আমাদের দুই ভাইয়ের কথা মনে হয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ফিরে আসার আর উপায় ছিল না।
১৫ আগস্টের পর অনেকে আমাদের আশ্রয় দিতে ভয় পেতেন। আবার অনেকে জীবনের অনেক ঝুঁকি নিয়েও আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। সবার কথা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না বলে আমি দুঃখিত। তবে তখন আমদের কেউ বাসা ভাড়া দিতে চাইত না। কয়েক মাস পর অনেক কষ্টে রেবা ফুফু (মেজো ফুফু) আরামবাগে আমাদের জন্য একটি বাসা ভাড়া নেন। ওই বাসায় আমরা কয়েক মাস থাকি। তত দিনে সেলিম কাকা, মারুফ কাকাসহ আমার মামারাও (আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও আবুল খায়ের আবদুল্লাহ) জীবন বাঁচাতে ভারতে পাড়ি দিয়েছেন। কারণ, বাংলাদেশে তাঁদের জীবন বাঁচানো অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
আরামবাগের বাসায় মঞ্জু ফুপার সাথে খেলা করতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনায় আমার মাথা ফেটে যায়। বাসায় ডাক্তার এনে মাথায় সেলাই দিতে হয়েছিল। মনে হয় হাসপাতালে নেওয়ার মতো পরিবেশ ছিল না, অথবা সাহস পাননি নিয়ে যেতে আমার দাদি-ফুফুরা।
যেহেতু চাচা-মামারা তত দিনে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, আমরাও প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলাম। প্রস্তুতিটা বেশ কঠিন ছিল। প্রথমত, বর্ডার দিয়ে যেতে হবে। কারণ, স্বাভাবিক উপায়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মোশতাক সরকার যদি ধরতে পারে, তাহলে মেরে ফেলবে। নিজের রাষ্ট্র থেকে যখন পালিয়ে বেড়াতে হয়, সে অভিজ্ঞতা যে কী পরিমাণ আতঙ্কের হতে পারে, সেটা তখন অনুধাবন না করলেও এখন বুঝতে পারি। চিন্তা করলে আমার পরিবারের সবার জন্য বুক ফেটে যায়। সারা জীবন এই দেশটা সৃষ্টি করতে গিয়ে এবং এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে, জেল-জুলুম আর নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন আমাদের দাদু, বঙ্গবন্ধু। শুধু তাই নয়, তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের অনেক রকম হয়রানিও করেছে পাকিস্তানি সরকার। আর সেই দেশ সৃষ্টির মাত্র তিন বছর পরই এই কী পরিণতি! এটা কী রকম বিচার!
দ্বিতীয়ত, বর্ডার পার হয়ে যেতে পারব কি–না, সেটার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। পথে পথে ভয়। প্রথম প্রচেষ্টায় আমরা যাওয়ার চেষ্টা করেও যেতে পারিনি। আগরতলা বর্ডারের একদম পাশে যে বাসায় আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম, তারা আমাদের গবাদিপশুর সাথে গোয়ালঘরে থাকতে দিয়েছিল। তারা আমাদের ধরিয়ে দেওয়া, আর লুট করার পরিকল্পনা করেছিল। দাদি আড়ি পেতে সেই পরিকল্পনার কথা শুনতে পেয়ে পরদিন সকালে জিনিসপত্র ওই বাসায় রেখে, মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আমাদের নিয়ে পালিয়ে ফেরত আসেন।
দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় আমরা বর্ডার পাড়ি দিই। এবার আমরা মেহেরপুর দিয়ে যাই। মেহেরপুরের সাবেক এমপি সহিউদ্দিন সাহেবের বাসায় আমরা আশ্রয় নিই। তাঁর ছেলে, ফরহাদ হোসেনের (বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী) সাথে আমি দুটি কুকুরের বাচ্চা লালু-ভুলুকে নিয়ে খেলা করি। ফরহাদ আমাদের বয়সী ছিল।
সব ধরনের যানবাহনেই চলতে হয়েছিল বর্ডার পার হতে গিয়ে। গরুর গাড়ি, নৌকা, এমনকি রাতের অন্ধকারে পায়ে হেঁটে ডোবানালাও অতিক্রম করতে হয়েছিল। সবচেয়ে কষ্ট হয়েছিল গরুর গাড়ি চড়া, ছাউনিঅলা গরুর গাড়ি। গরুর গাড়িতে অনেক ঝাঁকি খেতে হয়, মাথায় আঘাত লাগে। আমি কান্নাকাটি করছিলাম, আর সহ্য করতে পারছিলাম না। দাদি আর রেখা ফুফু (ছোট ফুফু) আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন যে, ‘আর একটু পথ, এই তো চলে এসেছি।’ কিন্তু পথ আর শেষ হয় না। সহ্য করেছিলাম শুধু জেনে যে, ওপারে পৌঁছালে বাবা-মাকে পাব। তখনো আমরা জানি না—বাবা-মা নেই। আমাদের বলা হয়েছিল বাবা-মা আহত হয়েছে। চিকিৎসার জন্য বিদেশে আছে। ওপারে পৌঁছালে সেলিম কাকা আর মারুফ কাকা আমাদের বাবা-মার কাছে নিয়ে যাবেন।
এমনকি ছোট্ট তাপসও আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। বলছিল, ‘পরশ দাদা আরেকটু কষ্ট করো। ওপারে গেলেই সেলিম কাকা, মারুফ কাকা আমাদের বাবা-মার কাছে নিয়ে যাবে।’ ওটাই ছিল আমার আর তাপসের একমাত্র ভরসা, একমাত্র আশার সম্বল।
ঠিক বর্ডারের কাছেই আমরা একটা চরের মতো জায়গায় আশ্রয় নিলাম। চারদিকে থইথই পানি; ঘন অন্ধকার রাত। আমরা অনেক ভয় পেয়েছিলাম। জায়গাটা ছিল অত্যন্ত দুর্গম। আমাদের সাথে সেলিম কাকা নজরুল নামে এক লোক ঠিক করে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক আমাদের সম্পূর্ণ সহায়তা করেছেন। উনি না থাকলে হয়তোবা আমরা আসতেই পারতাম না। একটা সময় ইঙ্গিত এল—এখন ফাঁকা আছে, আমাদের দৌড় দিতে হবে। তাপসকে কোলে নিয়ে আমরা রাতের অন্ধকারে দৌড় দিলাম। হাঁটু পর্যন্ত পানি অতিক্রম করে আমরা বিএসএফ বর্ডারে পৌঁছলাম। সেখানে একটা অফিসে আমাদের বসানো হলো। ওখানে উর্দি পরা মানুষজন ঘোরাফেরা করছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে অনেকক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হলো। তবে ওরা অনেক আদর-যত্ন করেছে। আমাদের নাশতাও খেতে দিয়েছিল।
 সেলিম কাকা আর হাসনাত মামাকে দেখে আমাদের আনন্দ আর ধরে না! আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। আমাদের সকল কষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটবে, এবং আমাদের বাবা-মার কাছে নিয়ে যাবে। আমাদের আর পায় কে? সেলিম কাকা আর হাসনাত মামাও আমাদের বুকে জড়িয়ে ভীষণ কান্না করছিলেন।
সেলিম কাকা আর হাসনাত মামাকে দেখে আমাদের আনন্দ আর ধরে না! আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। আমাদের সকল কষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটবে, এবং আমাদের বাবা-মার কাছে নিয়ে যাবে। আমাদের আর পায় কে? সেলিম কাকা আর হাসনাত মামাও আমাদের বুকে জড়িয়ে ভীষণ কান্না করছিলেন।
তাদের কান্না দেখে আশপাশের সবার চোখেই পানি এসেছিল সেই দিন। তাঁরা আমাদের কলকাতার বাঙ্গর নামক এলাকায়, সিনড্রেলার বাসায় নিয়ে এলেন। বাসাটি সংলগ্ন সিনড্রেলা নামে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ছিল। এ কারণেই বাসাটি সিনড্রেলার বাসা নামে পরিচিত। ওই বাসায় আমরা দুই ভাই বাবা-মাকে পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি সেখানে চাচি, মামি, কান্তা আপু ও শিশু সাদেকও (বর্তমান বরিশালের মেয়র) আছে।
কান্তা আপু আমাদের থেকে দু-তিন বছরের বড়। এ ছাড়া ওখানে তত দিনে বেশ কিছু আমাদের বাংলাদেশি আত্মীয়স্বজন, যাদের হয়রানি করছিল মোশতাক সরকার বিভিন্নভাবে, তাঁরাও পালিয়ে এসেছিলেন। অনেকে ছিলেন; কিন্তু বাবা-মা ছিল না।
আস্তে আস্তে আমাদের না পাওয়ার যন্ত্রণা সয়ে আসছিল কি না জানি না। কিন্তু আমার মধ্যে এক ধরনের বিরক্তি কাজ করছিল। আমি যেন বাবা-মাকে চাইতে চাইতে আর না পেতে পেতে অতিষ্ঠ। জিদ করে বাবা-মার কাছে যেতে চাওয়াও কমিয়ে দিই এক সময়। তবু অবচেতন মনে একটা আশা ছিল হয়তোবা বাবা-মা আসলেই লন্ডনে আছেন। কারণ, আমাদের সেটাই বলে সান্ত্বনা দেওয়া হতো।
আমি মনে হয়, ১৯৭৯ সালে দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত আশা করতাম বাবা-মাকে কোনো একদিন ফেরত পাব। একসময় বুঝতে পারলাম, বাবা-মা লন্ডনে থাকার কথাটা একটা অবাস্তব কল্পনা।
যেহেতু এক বাসায় বেশি মানুষ হয়ে গিয়েছিল, কিছু মাস পর আমরা বাসা বদলি করে আরেকটি বাসায় উঠি। ছোট্ট একটা তিন রুমের একতলা বাসা। পাশেই দুই কামরার অন্য একটা বাসা। ওখানে আরেকটি পরিবার থাকত। দুই বাসার মাঝখানে শুধু কলাপসিবল গেটের একটা দেয়াল। ওখানে এক সনাতন ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করত। ভদ্রলোক চাকরিজীবী ছিলেন, নিয়মতান্ত্রিক এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতেন। মৃদুভাষী ওই ভদ্রলোকের নামটা আমার মনে নেই। তবে তাঁর স্ত্রী, তন্দ্রা কাকি আমাদের পড়াতেন এবং অনেক আদর করতেন। তাঁদের দুই সন্তান—নান্টু আর মালি। মালি আমার বয়সী হবে, আর নান্টু আমার থেকে দু-এক বছরের বড়। শিগগিরই ওদের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওদের প্রতি মাসেই কোনো-না-কোনো ধর্মীয় উৎসব থাকত। প্রথমটাতে যাওয়ার পর আমার লোভ হয়ে গেল। আমি তারপর থেকে সবগুলো পূজার উৎসবে যেতে বায়না ধরতাম। দাদি ভয় পেতেন, যেতে দিতে চাইতেন না। আমিও জিদ করতাম। চাচি দাদিকে বুঝিয়ে ব্যবস্থা করে দিতেন। পূজা উৎসবগুলোর গানবাজনা আর আনন্দমুখর পরিবেশ আমার কাছে অসম্ভব ভালো লাগত।
কান্তা আপুও মাঝেমধ্যে আসতেন। আমরা একসঙ্গে খেলা করতাম। একদিন আমি, কান্তা আপু, তাপস আর নান্টু এক অভিযানে বের হলাম—আমরা চিরাচরিত গণ্ডি পেরিয়ে দূরে যে দমদম বিমানবন্দর দেখা যায়, ওখানে যাব। আমরা মাঠঘাট পেরিয়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছি। আমি সবার আগে আগে দৌড়াচ্ছিলাম। সামনে দেখি কালো চকচকে নিচু একটা পিচঢালা জায়গা। পা দিতেই হঠাৎ করে আমি অনুভব করলাম যে আমি কাদায় পা দিয়েছি। কিন্তু কাদা থেকে পা ওঠাতে পারছি না।
দেখলাম, যতই চেষ্টা করছি, আমি কাদার ভেতরে আরও ঢুকে যাচ্ছি। এরই মধ্যে কান্তা আপু, তাপস আর নান্টু এসে দেখে—আমি প্রায় কোমর পর্যন্ত ঢুকে গিয়েছি। তাপস আমার এই অবস্থা দেখে কেঁদেই ফেলল। ওর কান্না দেখে আমিও কান্না শুরু করলাম। কান্তা আপু আর নান্টু আমাদের মধ্যে বড়। এরা দুজন আমাকে ওঠানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। যেহেতু আমরা অভিযানের জন্য শর্টকাট পথ বেছে নিয়েছিলাম, জায়গাটা ভীষণ জনশূন্য ছিল। অনেক কসরত করে ওরা আমাকে চোরাবালি থেকে উদ্ধার করল। আমাকে তুলতে গিয়ে নান্টুর একটা পাও চোরাবালিতে পড়ে গিয়েছিল। পা ওঠাতে গিয়ে ওর স্যান্ডেলটা খোয়া যায়। এই ছিল আমার জীবনের প্রথম অভিযানের ফলাফল। আর দাদির কথার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি। ফেরার পথে আমরা সবাই খুবই ভীত ও মন খারাপ করছিলাম।
স্যান্ডেল হারিয়ে নান্টুর কী পেরেশানি! স্যান্ডেল–জোড়া গত মাসে পূজার সময় ওর বাবা কিনে দেন এবং সামনের বছরের পূজার আগে ওকে আর স্যান্ডেল কিনে দেওয়া হবে না। এই হচ্ছে ওর ডিলেমা। কথাটা শুনে আমি বুঝতে পারিনি প্রথমে। পরে বুঝলাম, ওর বাবা চাকরিজীবী, সীমিত আয়। তাই আর এক জোড়া স্যান্ডেল কিনতে ওর সামনের বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই নিয়মটা আমাকে ভাবায় এবং অবাকও করে।
আমরা একদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে সামনের ঘরে খেলছি। হঠাৎ দেখি, কে যেন বাইরের দরজায় করা নাড়ছে। শুনলাম পাশের ঘরে কান্নার আওয়াজ। দৌড়ে দাদির ঘরে গিয়ে দেখি দাদি একটা দাঁড়ি ও লম্বা চুলঅলা অল্প বয়সী লোককে ধরে কাঁদছেন। আমার বেশ খানিকটা সময় লাগল চিনতে যে লোকটা আমার মারুফ কাকা। ১৫ আগস্টের পর মারুফ কাকার সাথে মনে হয় ওই প্রথম আমার দেখা। মারুফ কাকাকে চেনাই যাচ্ছিল না। তাঁর যে জংলি অবস্থা! সারা শরীরে তাঁর দাগ আর ক্ষত। পরে শুনলাম মারুফ কাকা যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তিনি কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীতে যোগ দিয়ে বঙ্গবন্ধু-হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মারুফ কাকা’ ৭১ আর’ ৭৫-এ মোট দুবার যুদ্ধ করেছেন। শুধু’ ৭৫-এ তিনি দুবার তাঁর বাহিনী নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করেন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত দুবারই সেই প্রচেষ্টা বিফল হয়।
চাচি আমাদের বিভিন্নভাবে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। চাচির প্রধান লক্ষ্য ছিল, আমাদের যেন মন খারাপ না হয়; কান্নাকাটি না করি। সুভাষ (শেখ ফাহিম, এফবিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট) তখন ছয় মাসের হবে। সেলিম কাকা আর দাদির কাছে সুভাষকে রেখে আমাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সার্কাস দেখতে, অমিতাভ বচ্চনের সিনেমা দেখতে, আর শিশুপার্কে নিয়ে যেতেন। আমরা কোনো কিছুতেই ‘না’ করতাম না। চাচি আমাদের মায়ের মতোই ভালোবাসতেন। কারও বোঝার উপায় ছিল না যে, আমরা চাচির সন্তান নই। ২৪ ঘণ্টা চাচি আমাদের পেছনে সময় দিতেন। শুধু রাতে ঘুমাতাম দাদি আর রেখা ফুফুর সাথে। চাচি সারাক্ষণ আমাদের আগলে রাখতেন।
মায়ের শেষ কথাটা—‘আমার পরশ-তাপসকে তুমি দেইখো’, চাচি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।
একদিন চাচি আর রেখা ফুফু আমাদের নিয়ে বের হয়েছেন। ব্যস্ত রাস্তাঘাট। রেখা ফুফুও তখন ছোট, ১৫ বছর বয়স হবে। চাচি আর রেখা ফুফু আমাদের দুই ভাইয়ের হাত ধরে রাস্তা পার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। অস্থির আমি, চাচির হাত থেকে ছুটে দৌড় দিই একটা বাসের সামনে দিয়ে রাস্তার ওপারে। বাসটা বিকট আওয়াজ করে কষে ব্রেক করে। চাচি আর রেখা ফুফু সেদিন বড্ড ভয় পেয়েছিলেন। চাচি তো রীতিমতো কাঁপছিলেন। তিনি কেঁদে বলছিলেন, ‘আমার শাশুড়িকে আমি কি জবাব দিতাম, যদি কিছু হইতো।’
তখন বুঝলাম যে আমার এমনটা করা উচিত হয়নি। দেখতে দেখতে এভাবে প্রায় বছর খানেক পেরিয়ে যায়। আমাদেরও বাসা পরিবর্তন করার সময় চলে আসে। বাসা পরিবর্তন করা মানেই মায়ার টানাপোড়েন। আমার তন্দ্রা কাকি, আর নান্টুকে ছেড়ে আসতে খারাপ লাগছিল। আমরা বাঙ্গরের আরেকটা এলাকায় বাসা নিই। নতুন বাসাটা দোতলা। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, আর নতুন এলাকা। আশপাশের প্রতিবেশীরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আমাদের গ্রহণ করল। আমাদের মা-বাবা না থাকার ঘটনাটা মনে হয় ওরা জানত।
আমরা নিজেরাই তখনো সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত নই ব্যাপারটাতে। আমি শুধু এটুকু বুঝতাম যে, মানুষজন আমাদের একটু আলাদা চোখেই দেখত, আর আমাদের একটু বেশি মায়া করত। ওখানে আশপাশে অনেকগুলো পরিবার, বেশির ভাগই অল্পবয়স্ক মেয়েরা। চাচি ও রেখা ফুফুর সাথে ওদের ভালো সখ্য হয়ে গেল। আমার বয়সী মনে হয় তেমন ছেলেপেলে ছিল না বা থাকলেও ওদের সাথে আমার নান্টুর মতো বন্ধুত্ব হলো না।
তবে ওখানে পেলাম অন্যরকম আকর্ষণ। আমাদের ঠিক সামনের বাসাটা একটি বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি। এই বাসায় একটা তেজি সেবেল জার্মান শেফার্ড কুকুর ছিল, নাম মিকি। মিকিকে ঠিক সন্ধ্যার সময় বের করে রাস্তায় ছাড়ত। মিকি আমাদের গেটের সামনে আসত আর আমি ওকে বাসা থেকে এনে পাউরুটি খাওয়াতাম। আমার দারুণ ভালো লাগত। মিকিকে বল ছুড়ে মারলে ও বল নিয়ে আসতে পারত।
মিকিদের পাশের বাসাটা একটা দোতলা বাসা। ওই বাসায় একজন বয়স্ক মহিলা থাকতেন। তারও একটা জার্মান শেফার্ড কুকুর ছিল। ওর নামটা আমার মনে নেই। সাদা আর হালকা বাদামি এই শেফার্ডটার মধ্যে একটা আভিজাত্য ছিল। ও কারও সাথে খেলত না।
সেই বাসায় থাকতে আমি দুটি খরগোশ পালতাম। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, খরগোশ দুটির রক্তাক্ত অর্ধাংশ; ওপরের অংশটা শুধু আছে। বড়রা বোঝালেন, বিড়াল এসে খাঁচা ভেঙে আমার খরগোশ দুটি খেয়ে গেছে। আমি বিস্মিত হলাম আর সারা দিন কাঁদলাম। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি শিক্ষা নিলাম যে আমার আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল; ওদের ঘরের ভেতরে আরও নিরাপদে রাখা দরকার ছিল। এটা তখন আমার কল্পনার বাইরে ছিল যে, বাইরের বিড়াল খরগোশ খাবে।
আরও ছোটবেলা থেকেই আমার পশুপাখির প্রতি অনেক ঝোঁক। একবার আমি টুঙ্গিপাড়া থেকে আসার সময় জিদ ও বায়না করে কুকুরের বাচ্চা নিয়ে এসেছিলাম লঞ্চে করে ঢাকায়। ওরাও ১৫ আগস্টের শিকার হয়েছিল। আমার নানা, আবদুর রব সেরনিয়াবাত সাহেবের বাসায়ও দুটি লাল গরু ছিল। একবার আমি গরুগুলোকে ঘাস খাওয়াতে কাছে গিয়েছি। হঠাৎ একটা গরু ছুটে আমাকে তাড়া করেছিল এবং গুঁতাও মেরেছিল। মায়ের কী পেরেশানি! তিনি অনেক ভয় পেয়েছিলেন।
বঙ্গবন্ধু দাদার বাসায় যেতে পছন্দ করার অন্যতম কারণ ছিল, ওখানে অনেক ধরনের জীবজন্তু ছিল। কবুতর, কুকুর, মোরগ-মুরগি এবং অন্যান্য। একবার ওই বাসায় গিয়ে দেখি, একটা মুরগি অনেকগুলো বাচ্চা দিয়েছে। আমি ওদের নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে গেলাম এবং ওদের ছেড়ে আসতে চাচ্ছিলাম না। বায়না ধরলাম, আমারও ওগুলো লাগবে। মা তো মহা–মুসিবতে পড়লেন। আমি কিছুতেই ওদের পিছ ছাড়ি না। মা আমাকে একরকম জোর করে নিয়ে এলেন।
 আমি কাঁদতে কাঁদতে ও-বাসা থেকে চলে এলাম। বাসায় আসার পর বিকেলে দেখি আপন দাদি (বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব) মুরগি আর মুরগির বাচ্চাগুলো আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওই বাসায় আমি আপন দাদির অনেক ভক্ত ছিলাম। উনি আমাকে সবকিছুতে প্রশ্রয় দিতেন। আমার নিজের দাদিকে বাদ দিয়ে তাঁকেই ‘আপন দাদি’ বলে ডাকতাম। এই ছিল আমাদের মধুর সম্পর্ক।
আমি কাঁদতে কাঁদতে ও-বাসা থেকে চলে এলাম। বাসায় আসার পর বিকেলে দেখি আপন দাদি (বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব) মুরগি আর মুরগির বাচ্চাগুলো আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওই বাসায় আমি আপন দাদির অনেক ভক্ত ছিলাম। উনি আমাকে সবকিছুতে প্রশ্রয় দিতেন। আমার নিজের দাদিকে বাদ দিয়ে তাঁকেই ‘আপন দাদি’ বলে ডাকতাম। এই ছিল আমাদের মধুর সম্পর্ক।
আরেকজনের আমি খুব ভক্ত ছিলাম, যিনি হচ্ছেন হাসুমণি (জননেত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা)। তিনি আমার মায়ের শুধু মামাতো বোনই ছিলেন না, মায়ের বান্ধবীও ছিলেন। তাই হাসুমণির কোলে জয়কে (সজীব ওয়াজেদ জয়, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য) দেখলে আমি অভিযোগের সুরে জিজ্ঞেস করতাম, ‘হাসুমণির কোলে জয় কেন?’
হাসুমণির যেই গুনটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগত, তা হচ্ছে তাঁর মমত্ববোধ। প্রান্তিক মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ সমবেদনা ছিল। শিশুদের থেকে শুরু করে গৃহকর্মীদের প্রতি, এমনকি পশুপাখি ও জীবজন্তুর প্রতিও হাসুমণির প্রচণ্ড মায়া ছিল। এই মানবিক বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় তিনি সবার থেকে আলাদা। তিনি আমাদের বাচ্চাদের সাথে অত্যন্ত সদয় ছিলেন। বাচ্চাদের তিনি অনেক সময় দিতেন, এবং সত্যিকার অর্থে যত্নশীল ছিলেন শিশুদের মত ও মতামতের প্রতি।
একবার আমরা দিল্লি গেলাম। দাদি-নানি (আমার দাদি আর নানি দুই বোন), রেখা ফুফু আর আমরা দুই ভাই। হাসুমণি, রেহানা ফুফু আমাদের পেয়ে প্রচণ্ড আদর-যত্ন করলেন। তাঁরা মনে হয় আমাদের পেয়ে তাঁদের নিজ শোক সংবরণ করার শক্তি পেলেন। আমার সব দুষ্টামি তাঁরা মেনে নিতেন। জয় অনেক ঠান্ডা প্রকৃতির এবং সৃষ্টিশীল ছিল। সারাক্ষণ প্লেডো দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানাত। ওর ধৈর্য দেখে আমি অস্থির হয়ে যেতাম। আমি ওর সাথে দৌড়াদৌড়ি বা ছোঁয়া-ছুঁয়ি খেলতে চাইতাম। কিন্তু ওর ওসব খেলার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। অনেক শৃঙ্খলার সাথে জীবনযাপন করত। আমি অস্থির হয়ে ওর তৈরি করা সবকিছু ভেঙে দিতাম। ও রাগ করে আমার পিছে দৌড়াত, এতে আমার উদ্দেশ্যও হাসিল হতো। আমি পালাতাম। দাদি আর নানি আমাদের গোলমাল ঠেকাতে এসে মাঝেমধ্যে ব্যথাও পেতেন।
জয় সেটাতে অনেক বিচলিত হয়ে আমার নানিকে বলত, ‘আপনে কেন মাঝখানে এসে ব্যথা পেলেন?’ দাদিকে দেখিয়ে বলত, ‘উনি তো ঠেকাতে আসে না!’ হাসুমণি রেহানা ফুফু কিছুই বলত না। আমাদের এসব কার্যকলাপ দেখে মনে হয় মজা পেতেন। তাঁদের অনেক ধৈর্যশক্তি।
এভাবে প্রায় বছর তিনেক হয়ে গেল। আমিও অভ্যস্ত হয়ে গেলাম বাবা-মা ছাড়া জীবনে। এর মধ্যে বাংলাদেশে ফিরে আসার ব্যবস্থা নেওয়া হলো। আবার সীমানা পেরিয়ে ফিরে আসা। আমাদের বাঙ্গরের প্রতিবেশীরা অনেক মন খারাপ করল। ওদের সাথে আমাদের খুব আন্তরিকতা হয়ে গিয়েছিল, পরিবারের মতো। ঠিক হলো আমি, তাপস, রেখা ফুফু, দাদি আগে ফিরব। পরে চাচারা আসবে। ফিরে আসতে আসল কষ্টটা ছিল কঠোর বাস্তবতার অনুধাবন যে, বাবা-মা আসলে লন্ডনেও নাই; তাঁরা আকাশে হারিয়ে গেছে অজস্র তারার মাঝে। এই বাস্তবতায় মন মানতে না চাইলেও আমাদের কোনো কিছু করার ছিল না। কাকে কী বলব? কেউ তো ভালো নেই। খামাখা সবাইকে এ ব্যাপারে বিরক্ত করে লাভ কী? তাঁরা তো বাবা-মাকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না, পারলে তো আগেই দিতেন।
আমার মা গান গাইতে অনেক ভালোবাসতেন। আমাদের ঘুম পাড়ানোর সময় গাইতেন আঞ্জুমান আরা বেগমের সেই বিখ্যাত ঘুমপাড়ানি গান—‘খোকন সোনা বলি শোন/থাকবে না আর দুঃখ কোনো/মানুষ যদি হতে পারো।/এই কথাটি মনে রেখ/দুঃখীজনের সহায় থেকো।’ আমরা দুই ভাই বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে মানুষ হওয়ার সেই নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যেন ঘুমপাড়ানি এই গানের মধ্য দিয়ে, মা জীবনের সকল উপদেশ দিয়ে গেছেন। শুধু আফসোস মা দেখতে পারলেন না! দেখতে পারলেন না যে, আমরা পড়াশোনা শিখে তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করেছি।
মায়ের লেখাপড়ার প্রতি অনেক ঝোঁক ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এমএ পরীক্ষার ফল বের হয়। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাস করেছিলেন।
আগস্ট মাস এলে মানুষ জানতে চায়, বাবা-মা হারা আমাদের ছোটবেলা কীভাবে কেটেছে। কেমন ছিল আমাদের বেড়ে ওঠা? তাঁদের জন্যই আমার এই লেখা। অবশ্যই আমাদের বেড়ে ওঠা আর দশটা বাচ্চার মতো ছিল না। অত্যন্ত কোমল বয়সেই আমরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার। আমি এও জানি, নির্বাসিত শিশু হিসেবে আমাদের অভিজ্ঞতা এক আকর্ষণীয় একাডেমিক আলোচনা হিসেবে জায়গা পেতে পারে। তবুও বলব, তুলনামূলকভাবে অনেক এতিম বাচ্চার তুলনায় আমাদের শৈশব কেটেছে পরিবার-পরিজনের মায়া-মমতায়। আমার আত্মীয়-স্বজনদের আমাদের প্রতি মমত্ববোধ আর ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না। বরং আমরা একদিক দিয়ে ভাগ্যবান যে, বাবা-মায়ের ভালোবাসায় বঞ্চিত হলেও অন্য স্বজনদের স্নেহ-মমতা আমরা অনেক বেশিই পেয়েছি। যেটা কেউই পায় না। তবে এত আদর-যত্ন, ভালোবাসার মধ্যেও আমি অবশ্যই বাবা-মাকে খুঁজেছি।
মায়ের গাওয়া নির্মলা মিশ্রার আরেকটি গানের কথা মনে হয়—‘ও তোতা পাখীরে/শিকল খুলে উড়িয়ে দিব/আমার মাকে যদি এনে দাও/… ঘুমিয়ে ছিলাম মায়ের কোলে,/কখন যে মা গেল চলে? সবাই বলে ওই আকাশে/লুকিয়ে আছে খুঁজে নাও।’ যতই অনুভূতি রুদ্ধ করে রাখি, যতই খেলাধুলায় মেতে থাকি, শিশুরা যে মা-বাবাকে খুঁজে বেড়াবে—এটাই প্রকৃতির রীতি।
[বি. দ্র. : এই লেখা সম্পূর্ণরূপে আমার শিশুকালের স্মরণশক্তির ওপর ভিত্তি করে লেখা। তাই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই মর্মে যে, যদি ভুলবশত কাউকে আমি ভুলে গিয়ে থাকি। এখানে অনেক ঘটনা অসম্পূর্ণ ও আংশিক সত্য হতে পারে। কারণ, অপরিপক্ব এক ছয় বছরের শিশুর খণ্ড খণ্ড স্মৃতির ওপর এই কাহিনি গাথা। তাই পরিপূর্ণ সত্যতার কোনো দাবি এখানে আমি করছি না। ]
শেখ ফজলে শামস পরশ: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শহীদ শেখ ফজলুল হক মণি ও আরজু মণির বড় ছেলে। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ

খুব ভোরে প্রচণ্ড ভাঙচুরের আওয়াজে আমার ঘুম ভাঙে। উঠে দেখি মা নেই পাশে। বিছানায় শুধু আমরা দুই ভাই। জানালা দিয়ে ঝড়ের মতো গোলাগুলি হচ্ছে। গুলিগুলো দেয়াল ফুটো করে মেঝেতে আছড়ে পড়ছে। সিঁড়িঘরে অনেক কান্নাকাটির আওয়াজ, হইচই। আমরা দুই ভাই ভয়ে কাঁদতে কাঁদতে সিঁড়িঘরের দিকে গিয়ে দেখি বাবা-মা রক্তাক্ত অবস্থায় মাটিতে পড়া। মায়ের পা দুটো বাবার বুকের ওপর আড়াআড়ি রাখা। দাদির শাড়ির আঁচল মাটিতে লুটোপুটি যাচ্ছে, আর দাদি পাগলের মতো প্রলাপ বকছেন, দেয়ালে কপাল ঠুকছেন।
এ অবস্থায় উনি আমার বড় চাচিকে বললেন, ‘ফাতু (শেখ সেলিম কাকার সহধর্মিণী ফাতেমা চাচি), আরজুর পা দুটি মণির বুকের ওপর থেকে সরাও।’
সেলিম কাকা (শেখ সেলিম কাকা) আর চাচি বাবা-মার পাশে মেঝেতে হাঁটু গেড়ে বসে মাকে বাঁচানোর শেষ চেষ্টা করছেন। আর বাবা পুরোপুরি নিস্তেজ হয়ে পড়ে আছেন। মুখে কোনো কষ্টের চিহ্ন নাই। মনে হচ্ছে উনি যেন শান্তির নিদ্রায় বিভোর। শুধু গলায় কণ্ঠমণির নিচে চামড়া উঠে যাওয়ার একটা চিহ্ন। বাবার শরীরের অন্য কোথাও কোনো ক্ষত আমার মনে নাই। আমরা দুই ভাই কান্নাকাটি করছিলাম। মনে হয় আমরা ভয়েই কাঁদছিলাম; কারণ, মৃত্যু কাকে বলে তখনো আমরা জানি না। মৃত্যুর পর যে মানুষকে আর পাওয়া যায় না, সেটাও আমার জানা ছিল না। মৃত্যুর সাথে ওই আমার প্রথম পরিচয়। একসাথে অনেকগুলো মৃত্যু।
মায়ের মনে হয় অনেক কষ্ট হচ্ছিল আমাদের ফেলে যেতে। মা পানি খেতে চাচ্ছিলেন এবং বেঁচে থাকার চেষ্টা করছিলেন। বাইরে তখনো গুলির আওয়াজ থামে নাই। ভয়ানক গোলাগুলির আওয়াজ আর তার সঙ্গে জানালা ভাঙচুরের আওয়াজ।
মা চাচিকে বললেন, ‘ফাতু আমাকে বাঁচাও। আমার পরশ-তাপস! ওদেরকে তুমি দেইখো।’
ওটাই বোধ হয় মায়ের শেষ কথা। এর পর কী হলো আমি জানি না। গুলির আওয়াজ অনেক বেড়ে যাচ্ছিল এবং কারা যেন এদিকে আবার আসছিল। আমার চাচি তখন আমাদের নিয়ে তাঁর ড্রেসিংরুমে পালালেন। আমাদের মেঝেতে শুইয়ে রেখেছিলেন, যাতে গুলি না লাগে। গুলি মনে হয় বাথরুমের জানালা দিয়ে ড্রেসিংরুমেও ঢুকে যাচ্ছিল।
এর পর আর বাবা-মার সঙ্গে আমাদের আর দেখা হয় নাই। শুনেছি সেলিম কাকা একটা গাড়িতে করে মাকে হাসপাতালে নিয়ে গিয়েছিলেন। আর মারুফ কাকা অন্য এক গাড়িতে বাবাকে হাসপাতালে নিয়ে যান।
এর পর সবকিছু ঠান্ডা হয়ে যাওয়ার পর আমরা দুই ভাই, চাচি, দাদি, আর রেখা ফুফু এক কাপড়ে আমাদের বাসা থেকে বের হয়ে যাই। তখনো বুঝি নাই যে, ওটাই নিজেদের বাসা থেকে আমাদের শেষ প্রস্থান। আর কখনো ওই বাসায় ফিরতে পারব না। আমার বয়স তখন পাঁচ বছর, আর আমার ভাই তাপসের বয়স চার বছর। আমাদের বাসাটা ছিল ধানমন্ডি ১৩ নম্বর রোডে একটা কানাগলির রাস্তায়। বাসা থেকে বের হয়ে পাশেই ছিল এক বিদেশি রাষ্ট্রদূত ভবন। আমরা সেখানেই আশ্রয় নিই। ওখান থেকে আমরা দেখতে পাই, আমাদের বাসায় আর্মিদের আনাগোনা, লুটতরাজ। এর পর শুরু হয় আমাদের ভবঘুরে জীবনযাপন; একেক দিন একেক বাসায়।
কোনো বাসায় দুদিন, কোনো বাসায় চার দিন। আশ্রয়ার্থী হিসেবে এভাবেই চলতে থাকে বেশ কয়েক মাস। আমার কোনো ধারণা ছিল না, কেন আমরা নিজের বাসায় ফেরত যেতে পারছি না। পরে দাদি-চাচিদের মাধ্যমে বুঝলাম যে আর্মিরা আমাদের খুঁজছিল। কয়েকটি বাসায় আর্মিরা আমাদের খুঁজতেও এসেছিল। ভাগ্যিস আমরা সময়মতো সেই বাসা থেকে পালিয়ে অন্য বাসায় আশ্রয় নিয়েছিলাম।
মাহুতটুলিতে মঞ্জু খালার বাসায় আমরা মনে হয় বেশ কিছুদিন ছিলাম। মঞ্জু খালা আমাদের পেয়ে অস্থির! আদর-যত্নেই ছিলাম। কিন্তু নিরাপত্তার অভাবে সে বাসায়ও শান্তিতে থাকতে পারিনি। চলে আসার সময় গেটের সামনে দাঁড়িয়ে মঞ্জু খালা ভীষণ কেঁদেছিলেন। তখনো জানতাম না ওই কান্নার আড়ালের অন্তর্নিহিত কারণ।
এখানে উল্লেখ করা প্রয়োজন, মঞ্জু খালাও ১৫ আগস্ট তাঁর বাবা (আবদুর রব সেরনিয়াবাত), দুই বোন (আমার মা ও বেবি খালা), ভাই (আরিফ মামা) ও চার বছরের ভাতিজাকে (সুকান্ত বাবু) হারিয়েছেন। তারপর আবার আমাদের চোখের সামনে দেখতে পাওয়াই তো ওনাদের জন্য প্রচণ্ড মানসিক চাপ ছিল।
আমার চাচির আব্বা, মরহুম সুলতান আহমেদ চৌধুরীর (শেখ সেলিম কাকার শ্বশুর) বাসায়ও আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম। সেই বাসায় আর্মিরা রেইডও করেছিল। চাচির বড়বোন, আনু খালার পাঁচ বছর বয়সী সন্তান লিমাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়ার চেষ্টাও করেছিল।
পরে অনেক কসরত করে এবং ধস্তাধস্তি করে লিমাকে ছিনিয়ে আনতে সক্ষম হয় ওর বাবা আজাদ আংকেল। চাচির মেজো ভাই, বাচ্চু মামাকেও আর্মিরা তুলে নিয়ে যায়। বাচ্চু মামা, সেলিম কাকা, মারুফ কাকাদের সীমানা পার করে দিয়ে আসার পরই তাঁকে বাসা থেকে তুলে নিয়ে যান কর্নেল শাহরিয়ার। আর তাঁকে পাওয়া যায়নি। এমনকি তাঁর লাশটাও ওরা ফেরত দেয়নি।
সবাই তখন সারাক্ষণ শুধু কাঁদত। কারও সন্তান হারানোর ব্যথা, কারও ভাইবোন হারানোর কষ্ট, আর আমাদের বাবা-মা হারানোর অন্তহীন কান্না। তবে কেউ কারও সামনে কাঁদতে পারত না। আড়ালে গিয়ে বোবা কান্না কাঁদত। আমাদের সামনে সবাই কান্না আড়াল করে ফেলত। কারণ, তখনো আমদের বলা হয়নি যে, আমাদের বাবা-মা আর নেই। এভাবেই জীবননাশের হুমকি আর ভয়ভীতিকে সঙ্গী করে আমাদের শোকাহত পরিবারের জীবনের গাড়ি চলতে থাকে।
সেলিম কাকা আর মারুফ কাকার জীবনে তখন চরম ঝুঁকি। মারুফ কাকা তখন খুনিদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করার উদ্দেশ্যে কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীতে যোগ দিতে মেঘালয় চলে যান। সেলিম কাকাকে তো গুলিই করা হয়েছিল। অল্পের জন্য অলৌকিকভাবে তিনি বেঁচে যান। শুনেছি খুনিরা যখন বাবাকে মারতে আসে, চাচি সেলিম কাকাকে ঘুম থেকে উঠিয়ে খবর দেন। সেলিম কাকা হুড়মুড় করে গিয়ে দেখে ওরা বন্দুক তাক করে আছে বাবার দিকে। সেলিম কাকা ওদের ধাক্কা দিলে ওরাও তাকে ধাক্কা দিয়ে সিঁড়িঘরের কোনায় ফেলে দেয়।
ঠিক তখনই ওরা গুলি শুরু করে। রুমের কোনায় এবং নিচে পড়েছিলেন বলে হয়তো–বা গুলি তাঁর গায়ে লাগেনি। ওই মুহূর্তে মা তখন রুম থেকে বের হয়ে এসে বাবার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়ান। আমার মা মনে হয় বাবাকে অনেক বেশি ভালোবাসতেন। তাই প্রবৃত্তির বশবর্তী হয়েই মা বাবার সামনে ঢাল হয়ে দাঁড়িয়ে পড়েন। সেই মুহূর্তে তিনি আমাদের কথাও ভাবেননি। মা স্বামীর প্রতি নিঃস্বার্থ ভালোবাসার উদাহরণ রেখে গেছেন। হয়তো গুলি লাগার পর তাঁর আমাদের দুই ভাইয়ের কথা মনে হয়েছে। কিন্তু ততক্ষণে অনেক দেরি হয়ে গেছে। ফিরে আসার আর উপায় ছিল না।
১৫ আগস্টের পর অনেকে আমাদের আশ্রয় দিতে ভয় পেতেন। আবার অনেকে জীবনের অনেক ঝুঁকি নিয়েও আমাদের আশ্রয় দিয়েছেন। সবার কথা এখানে উল্লেখ করা সম্ভব হলো না বলে আমি দুঃখিত। তবে তখন আমদের কেউ বাসা ভাড়া দিতে চাইত না। কয়েক মাস পর অনেক কষ্টে রেবা ফুফু (মেজো ফুফু) আরামবাগে আমাদের জন্য একটি বাসা ভাড়া নেন। ওই বাসায় আমরা কয়েক মাস থাকি। তত দিনে সেলিম কাকা, মারুফ কাকাসহ আমার মামারাও (আবুল হাসনাত আবদুল্লাহ ও আবুল খায়ের আবদুল্লাহ) জীবন বাঁচাতে ভারতে পাড়ি দিয়েছেন। কারণ, বাংলাদেশে তাঁদের জীবন বাঁচানো অনেক কঠিন হয়ে দাঁড়িয়েছিল।
আরামবাগের বাসায় মঞ্জু ফুপার সাথে খেলা করতে গিয়ে একটা দুর্ঘটনায় আমার মাথা ফেটে যায়। বাসায় ডাক্তার এনে মাথায় সেলাই দিতে হয়েছিল। মনে হয় হাসপাতালে নেওয়ার মতো পরিবেশ ছিল না, অথবা সাহস পাননি নিয়ে যেতে আমার দাদি-ফুফুরা।
যেহেতু চাচা-মামারা তত দিনে ভারতে আশ্রয় নিয়েছেন, আমরাও প্রস্তুতি নেওয়া শুরু করলাম। প্রস্তুতিটা বেশ কঠিন ছিল। প্রথমত, বর্ডার দিয়ে যেতে হবে। কারণ, স্বাভাবিক উপায়ে যাওয়ার কোনো প্রশ্নই ওঠে না। মোশতাক সরকার যদি ধরতে পারে, তাহলে মেরে ফেলবে। নিজের রাষ্ট্র থেকে যখন পালিয়ে বেড়াতে হয়, সে অভিজ্ঞতা যে কী পরিমাণ আতঙ্কের হতে পারে, সেটা তখন অনুধাবন না করলেও এখন বুঝতে পারি। চিন্তা করলে আমার পরিবারের সবার জন্য বুক ফেটে যায়। সারা জীবন এই দেশটা সৃষ্টি করতে গিয়ে এবং এ দেশের মানুষের অধিকার আদায়ের সংগ্রামে, জেল-জুলুম আর নির্যাতনের স্বীকার হয়েছেন আমাদের দাদু, বঙ্গবন্ধু। শুধু তাই নয়, তাঁর পরিবারের অন্য সদস্যদের অনেক রকম হয়রানিও করেছে পাকিস্তানি সরকার। আর সেই দেশ সৃষ্টির মাত্র তিন বছর পরই এই কী পরিণতি! এটা কী রকম বিচার!
দ্বিতীয়ত, বর্ডার পার হয়ে যেতে পারব কি–না, সেটার কোনো নিশ্চয়তা ছিল না। পথে পথে ভয়। প্রথম প্রচেষ্টায় আমরা যাওয়ার চেষ্টা করেও যেতে পারিনি। আগরতলা বর্ডারের একদম পাশে যে বাসায় আমরা আশ্রয় নিয়েছিলাম, তারা আমাদের গবাদিপশুর সাথে গোয়ালঘরে থাকতে দিয়েছিল। তারা আমাদের ধরিয়ে দেওয়া, আর লুট করার পরিকল্পনা করেছিল। দাদি আড়ি পেতে সেই পরিকল্পনার কথা শুনতে পেয়ে পরদিন সকালে জিনিসপত্র ওই বাসায় রেখে, মিথ্যা অজুহাত দেখিয়ে আমাদের নিয়ে পালিয়ে ফেরত আসেন।
দ্বিতীয় প্রচেষ্টায় আমরা বর্ডার পাড়ি দিই। এবার আমরা মেহেরপুর দিয়ে যাই। মেহেরপুরের সাবেক এমপি সহিউদ্দিন সাহেবের বাসায় আমরা আশ্রয় নিই। তাঁর ছেলে, ফরহাদ হোসেনের (বর্তমান জনপ্রশাসন প্রতিমন্ত্রী) সাথে আমি দুটি কুকুরের বাচ্চা লালু-ভুলুকে নিয়ে খেলা করি। ফরহাদ আমাদের বয়সী ছিল।
সব ধরনের যানবাহনেই চলতে হয়েছিল বর্ডার পার হতে গিয়ে। গরুর গাড়ি, নৌকা, এমনকি রাতের অন্ধকারে পায়ে হেঁটে ডোবানালাও অতিক্রম করতে হয়েছিল। সবচেয়ে কষ্ট হয়েছিল গরুর গাড়ি চড়া, ছাউনিঅলা গরুর গাড়ি। গরুর গাড়িতে অনেক ঝাঁকি খেতে হয়, মাথায় আঘাত লাগে। আমি কান্নাকাটি করছিলাম, আর সহ্য করতে পারছিলাম না। দাদি আর রেখা ফুফু (ছোট ফুফু) আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিলেন যে, ‘আর একটু পথ, এই তো চলে এসেছি।’ কিন্তু পথ আর শেষ হয় না। সহ্য করেছিলাম শুধু জেনে যে, ওপারে পৌঁছালে বাবা-মাকে পাব। তখনো আমরা জানি না—বাবা-মা নেই। আমাদের বলা হয়েছিল বাবা-মা আহত হয়েছে। চিকিৎসার জন্য বিদেশে আছে। ওপারে পৌঁছালে সেলিম কাকা আর মারুফ কাকা আমাদের বাবা-মার কাছে নিয়ে যাবেন।
এমনকি ছোট্ট তাপসও আমাকে সান্ত্বনা দিচ্ছিল। বলছিল, ‘পরশ দাদা আরেকটু কষ্ট করো। ওপারে গেলেই সেলিম কাকা, মারুফ কাকা আমাদের বাবা-মার কাছে নিয়ে যাবে।’ ওটাই ছিল আমার আর তাপসের একমাত্র ভরসা, একমাত্র আশার সম্বল।
ঠিক বর্ডারের কাছেই আমরা একটা চরের মতো জায়গায় আশ্রয় নিলাম। চারদিকে থইথই পানি; ঘন অন্ধকার রাত। আমরা অনেক ভয় পেয়েছিলাম। জায়গাটা ছিল অত্যন্ত দুর্গম। আমাদের সাথে সেলিম কাকা নজরুল নামে এক লোক ঠিক করে দিয়েছিলেন। ভদ্রলোক আমাদের সম্পূর্ণ সহায়তা করেছেন। উনি না থাকলে হয়তোবা আমরা আসতেই পারতাম না। একটা সময় ইঙ্গিত এল—এখন ফাঁকা আছে, আমাদের দৌড় দিতে হবে। তাপসকে কোলে নিয়ে আমরা রাতের অন্ধকারে দৌড় দিলাম। হাঁটু পর্যন্ত পানি অতিক্রম করে আমরা বিএসএফ বর্ডারে পৌঁছলাম। সেখানে একটা অফিসে আমাদের বসানো হলো। ওখানে উর্দি পরা মানুষজন ঘোরাফেরা করছে। সিদ্ধান্ত গ্রহণ ও আনুষ্ঠানিকতা সম্পন্ন করতে অনেকক্ষণ আমাদের অপেক্ষা করতে হলো। তবে ওরা অনেক আদর-যত্ন করেছে। আমাদের নাশতাও খেতে দিয়েছিল।
 সেলিম কাকা আর হাসনাত মামাকে দেখে আমাদের আনন্দ আর ধরে না! আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। আমাদের সকল কষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটবে, এবং আমাদের বাবা-মার কাছে নিয়ে যাবে। আমাদের আর পায় কে? সেলিম কাকা আর হাসনাত মামাও আমাদের বুকে জড়িয়ে ভীষণ কান্না করছিলেন।
সেলিম কাকা আর হাসনাত মামাকে দেখে আমাদের আনন্দ আর ধরে না! আমরা যেন আকাশের চাঁদ হাতে পেয়েছি। আমাদের সকল কষ্টের পরিসমাপ্তি ঘটবে, এবং আমাদের বাবা-মার কাছে নিয়ে যাবে। আমাদের আর পায় কে? সেলিম কাকা আর হাসনাত মামাও আমাদের বুকে জড়িয়ে ভীষণ কান্না করছিলেন।
তাদের কান্না দেখে আশপাশের সবার চোখেই পানি এসেছিল সেই দিন। তাঁরা আমাদের কলকাতার বাঙ্গর নামক এলাকায়, সিনড্রেলার বাসায় নিয়ে এলেন। বাসাটি সংলগ্ন সিনড্রেলা নামে একটা ডিপার্টমেন্টাল স্টোর ছিল। এ কারণেই বাসাটি সিনড্রেলার বাসা নামে পরিচিত। ওই বাসায় আমরা দুই ভাই বাবা-মাকে পাওয়ার স্বপ্ন নিয়ে ঢুকলাম। ঢুকে দেখি সেখানে চাচি, মামি, কান্তা আপু ও শিশু সাদেকও (বর্তমান বরিশালের মেয়র) আছে।
কান্তা আপু আমাদের থেকে দু-তিন বছরের বড়। এ ছাড়া ওখানে তত দিনে বেশ কিছু আমাদের বাংলাদেশি আত্মীয়স্বজন, যাদের হয়রানি করছিল মোশতাক সরকার বিভিন্নভাবে, তাঁরাও পালিয়ে এসেছিলেন। অনেকে ছিলেন; কিন্তু বাবা-মা ছিল না।
আস্তে আস্তে আমাদের না পাওয়ার যন্ত্রণা সয়ে আসছিল কি না জানি না। কিন্তু আমার মধ্যে এক ধরনের বিরক্তি কাজ করছিল। আমি যেন বাবা-মাকে চাইতে চাইতে আর না পেতে পেতে অতিষ্ঠ। জিদ করে বাবা-মার কাছে যেতে চাওয়াও কমিয়ে দিই এক সময়। তবু অবচেতন মনে একটা আশা ছিল হয়তোবা বাবা-মা আসলেই লন্ডনে আছেন। কারণ, আমাদের সেটাই বলে সান্ত্বনা দেওয়া হতো।
আমি মনে হয়, ১৯৭৯ সালে দেশে ফেরার আগ পর্যন্ত আশা করতাম বাবা-মাকে কোনো একদিন ফেরত পাব। একসময় বুঝতে পারলাম, বাবা-মা লন্ডনে থাকার কথাটা একটা অবাস্তব কল্পনা।
যেহেতু এক বাসায় বেশি মানুষ হয়ে গিয়েছিল, কিছু মাস পর আমরা বাসা বদলি করে আরেকটি বাসায় উঠি। ছোট্ট একটা তিন রুমের একতলা বাসা। পাশেই দুই কামরার অন্য একটা বাসা। ওখানে আরেকটি পরিবার থাকত। দুই বাসার মাঝখানে শুধু কলাপসিবল গেটের একটা দেয়াল। ওখানে এক সনাতন ব্রাহ্মণ পরিবার বাস করত। ভদ্রলোক চাকরিজীবী ছিলেন, নিয়মতান্ত্রিক এবং সুশৃঙ্খল জীবনযাপন করতেন। মৃদুভাষী ওই ভদ্রলোকের নামটা আমার মনে নেই। তবে তাঁর স্ত্রী, তন্দ্রা কাকি আমাদের পড়াতেন এবং অনেক আদর করতেন। তাঁদের দুই সন্তান—নান্টু আর মালি। মালি আমার বয়সী হবে, আর নান্টু আমার থেকে দু-এক বছরের বড়। শিগগিরই ওদের সাথে আমার বন্ধুত্ব হয়ে গেল। ওদের প্রতি মাসেই কোনো-না-কোনো ধর্মীয় উৎসব থাকত। প্রথমটাতে যাওয়ার পর আমার লোভ হয়ে গেল। আমি তারপর থেকে সবগুলো পূজার উৎসবে যেতে বায়না ধরতাম। দাদি ভয় পেতেন, যেতে দিতে চাইতেন না। আমিও জিদ করতাম। চাচি দাদিকে বুঝিয়ে ব্যবস্থা করে দিতেন। পূজা উৎসবগুলোর গানবাজনা আর আনন্দমুখর পরিবেশ আমার কাছে অসম্ভব ভালো লাগত।
কান্তা আপুও মাঝেমধ্যে আসতেন। আমরা একসঙ্গে খেলা করতাম। একদিন আমি, কান্তা আপু, তাপস আর নান্টু এক অভিযানে বের হলাম—আমরা চিরাচরিত গণ্ডি পেরিয়ে দূরে যে দমদম বিমানবন্দর দেখা যায়, ওখানে যাব। আমরা মাঠঘাট পেরিয়ে যাচ্ছি তো যাচ্ছি। আমি সবার আগে আগে দৌড়াচ্ছিলাম। সামনে দেখি কালো চকচকে নিচু একটা পিচঢালা জায়গা। পা দিতেই হঠাৎ করে আমি অনুভব করলাম যে আমি কাদায় পা দিয়েছি। কিন্তু কাদা থেকে পা ওঠাতে পারছি না।
দেখলাম, যতই চেষ্টা করছি, আমি কাদার ভেতরে আরও ঢুকে যাচ্ছি। এরই মধ্যে কান্তা আপু, তাপস আর নান্টু এসে দেখে—আমি প্রায় কোমর পর্যন্ত ঢুকে গিয়েছি। তাপস আমার এই অবস্থা দেখে কেঁদেই ফেলল। ওর কান্না দেখে আমিও কান্না শুরু করলাম। কান্তা আপু আর নান্টু আমাদের মধ্যে বড়। এরা দুজন আমাকে ওঠানোর আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগল। যেহেতু আমরা অভিযানের জন্য শর্টকাট পথ বেছে নিয়েছিলাম, জায়গাটা ভীষণ জনশূন্য ছিল। অনেক কসরত করে ওরা আমাকে চোরাবালি থেকে উদ্ধার করল। আমাকে তুলতে গিয়ে নান্টুর একটা পাও চোরাবালিতে পড়ে গিয়েছিল। পা ওঠাতে গিয়ে ওর স্যান্ডেলটা খোয়া যায়। এই ছিল আমার জীবনের প্রথম অভিযানের ফলাফল। আর দাদির কথার অবাধ্য হওয়ার শাস্তি। ফেরার পথে আমরা সবাই খুবই ভীত ও মন খারাপ করছিলাম।
স্যান্ডেল হারিয়ে নান্টুর কী পেরেশানি! স্যান্ডেল–জোড়া গত মাসে পূজার সময় ওর বাবা কিনে দেন এবং সামনের বছরের পূজার আগে ওকে আর স্যান্ডেল কিনে দেওয়া হবে না। এই হচ্ছে ওর ডিলেমা। কথাটা শুনে আমি বুঝতে পারিনি প্রথমে। পরে বুঝলাম, ওর বাবা চাকরিজীবী, সীমিত আয়। তাই আর এক জোড়া স্যান্ডেল কিনতে ওর সামনের বছর পর্যন্ত অপেক্ষা করতে হবে। এই নিয়মটা আমাকে ভাবায় এবং অবাকও করে।
আমরা একদিন দুপুরবেলা খাওয়া-দাওয়া সেরে সামনের ঘরে খেলছি। হঠাৎ দেখি, কে যেন বাইরের দরজায় করা নাড়ছে। শুনলাম পাশের ঘরে কান্নার আওয়াজ। দৌড়ে দাদির ঘরে গিয়ে দেখি দাদি একটা দাঁড়ি ও লম্বা চুলঅলা অল্প বয়সী লোককে ধরে কাঁদছেন। আমার বেশ খানিকটা সময় লাগল চিনতে যে লোকটা আমার মারুফ কাকা। ১৫ আগস্টের পর মারুফ কাকার সাথে মনে হয় ওই প্রথম আমার দেখা। মারুফ কাকাকে চেনাই যাচ্ছিল না। তাঁর যে জংলি অবস্থা! সারা শরীরে তাঁর দাগ আর ক্ষত। পরে শুনলাম মারুফ কাকা যুদ্ধে গিয়েছিলেন। তিনি কাদের সিদ্দিকীর বাহিনীতে যোগ দিয়ে বঙ্গবন্ধু-হত্যার প্রতিশোধ নেওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। মারুফ কাকা’ ৭১ আর’ ৭৫-এ মোট দুবার যুদ্ধ করেছেন। শুধু’ ৭৫-এ তিনি দুবার তাঁর বাহিনী নিয়ে বাংলাদেশে প্রবেশের চেষ্টা করেন প্রতিশোধ নেওয়ার জন্য। দুর্ভাগ্যবশত দুবারই সেই প্রচেষ্টা বিফল হয়।
চাচি আমাদের বিভিন্নভাবে ভুলিয়ে রাখতে চেষ্টা করতেন। চাচির প্রধান লক্ষ্য ছিল, আমাদের যেন মন খারাপ না হয়; কান্নাকাটি না করি। সুভাষ (শেখ ফাহিম, এফবিসিসিআইয়ের প্রেসিডেন্ট) তখন ছয় মাসের হবে। সেলিম কাকা আর দাদির কাছে সুভাষকে রেখে আমাদের সান্ত্বনা দেওয়ার জন্য সার্কাস দেখতে, অমিতাভ বচ্চনের সিনেমা দেখতে, আর শিশুপার্কে নিয়ে যেতেন। আমরা কোনো কিছুতেই ‘না’ করতাম না। চাচি আমাদের মায়ের মতোই ভালোবাসতেন। কারও বোঝার উপায় ছিল না যে, আমরা চাচির সন্তান নই। ২৪ ঘণ্টা চাচি আমাদের পেছনে সময় দিতেন। শুধু রাতে ঘুমাতাম দাদি আর রেখা ফুফুর সাথে। চাচি সারাক্ষণ আমাদের আগলে রাখতেন।
মায়ের শেষ কথাটা—‘আমার পরশ-তাপসকে তুমি দেইখো’, চাচি অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছেন।
একদিন চাচি আর রেখা ফুফু আমাদের নিয়ে বের হয়েছেন। ব্যস্ত রাস্তাঘাট। রেখা ফুফুও তখন ছোট, ১৫ বছর বয়স হবে। চাচি আর রেখা ফুফু আমাদের দুই ভাইয়ের হাত ধরে রাস্তা পার হওয়ার প্রস্তুতি নিচ্ছিলেন। অস্থির আমি, চাচির হাত থেকে ছুটে দৌড় দিই একটা বাসের সামনে দিয়ে রাস্তার ওপারে। বাসটা বিকট আওয়াজ করে কষে ব্রেক করে। চাচি আর রেখা ফুফু সেদিন বড্ড ভয় পেয়েছিলেন। চাচি তো রীতিমতো কাঁপছিলেন। তিনি কেঁদে বলছিলেন, ‘আমার শাশুড়িকে আমি কি জবাব দিতাম, যদি কিছু হইতো।’
তখন বুঝলাম যে আমার এমনটা করা উচিত হয়নি। দেখতে দেখতে এভাবে প্রায় বছর খানেক পেরিয়ে যায়। আমাদেরও বাসা পরিবর্তন করার সময় চলে আসে। বাসা পরিবর্তন করা মানেই মায়ার টানাপোড়েন। আমার তন্দ্রা কাকি, আর নান্টুকে ছেড়ে আসতে খারাপ লাগছিল। আমরা বাঙ্গরের আরেকটা এলাকায় বাসা নিই। নতুন বাসাটা দোতলা। বেশ পরিষ্কার-পরিচ্ছন্ন পরিবেশ, আর নতুন এলাকা। আশপাশের প্রতিবেশীরা বন্ধুত্বপূর্ণভাবে আমাদের গ্রহণ করল। আমাদের মা-বাবা না থাকার ঘটনাটা মনে হয় ওরা জানত।
আমরা নিজেরাই তখনো সম্পূর্ণরূপে নিশ্চিত নই ব্যাপারটাতে। আমি শুধু এটুকু বুঝতাম যে, মানুষজন আমাদের একটু আলাদা চোখেই দেখত, আর আমাদের একটু বেশি মায়া করত। ওখানে আশপাশে অনেকগুলো পরিবার, বেশির ভাগই অল্পবয়স্ক মেয়েরা। চাচি ও রেখা ফুফুর সাথে ওদের ভালো সখ্য হয়ে গেল। আমার বয়সী মনে হয় তেমন ছেলেপেলে ছিল না বা থাকলেও ওদের সাথে আমার নান্টুর মতো বন্ধুত্ব হলো না।
তবে ওখানে পেলাম অন্যরকম আকর্ষণ। আমাদের ঠিক সামনের বাসাটা একটি বহুতল ফ্ল্যাট বাড়ি। এই বাসায় একটা তেজি সেবেল জার্মান শেফার্ড কুকুর ছিল, নাম মিকি। মিকিকে ঠিক সন্ধ্যার সময় বের করে রাস্তায় ছাড়ত। মিকি আমাদের গেটের সামনে আসত আর আমি ওকে বাসা থেকে এনে পাউরুটি খাওয়াতাম। আমার দারুণ ভালো লাগত। মিকিকে বল ছুড়ে মারলে ও বল নিয়ে আসতে পারত।
মিকিদের পাশের বাসাটা একটা দোতলা বাসা। ওই বাসায় একজন বয়স্ক মহিলা থাকতেন। তারও একটা জার্মান শেফার্ড কুকুর ছিল। ওর নামটা আমার মনে নেই। সাদা আর হালকা বাদামি এই শেফার্ডটার মধ্যে একটা আভিজাত্য ছিল। ও কারও সাথে খেলত না।
সেই বাসায় থাকতে আমি দুটি খরগোশ পালতাম। একদিন সকালে ঘুম থেকে উঠে দেখি, খরগোশ দুটির রক্তাক্ত অর্ধাংশ; ওপরের অংশটা শুধু আছে। বড়রা বোঝালেন, বিড়াল এসে খাঁচা ভেঙে আমার খরগোশ দুটি খেয়ে গেছে। আমি বিস্মিত হলাম আর সারা দিন কাঁদলাম। এই অভিজ্ঞতা থেকে আমি শিক্ষা নিলাম যে আমার আরও সতর্ক থাকা উচিত ছিল; ওদের ঘরের ভেতরে আরও নিরাপদে রাখা দরকার ছিল। এটা তখন আমার কল্পনার বাইরে ছিল যে, বাইরের বিড়াল খরগোশ খাবে।
আরও ছোটবেলা থেকেই আমার পশুপাখির প্রতি অনেক ঝোঁক। একবার আমি টুঙ্গিপাড়া থেকে আসার সময় জিদ ও বায়না করে কুকুরের বাচ্চা নিয়ে এসেছিলাম লঞ্চে করে ঢাকায়। ওরাও ১৫ আগস্টের শিকার হয়েছিল। আমার নানা, আবদুর রব সেরনিয়াবাত সাহেবের বাসায়ও দুটি লাল গরু ছিল। একবার আমি গরুগুলোকে ঘাস খাওয়াতে কাছে গিয়েছি। হঠাৎ একটা গরু ছুটে আমাকে তাড়া করেছিল এবং গুঁতাও মেরেছিল। মায়ের কী পেরেশানি! তিনি অনেক ভয় পেয়েছিলেন।
বঙ্গবন্ধু দাদার বাসায় যেতে পছন্দ করার অন্যতম কারণ ছিল, ওখানে অনেক ধরনের জীবজন্তু ছিল। কবুতর, কুকুর, মোরগ-মুরগি এবং অন্যান্য। একবার ওই বাসায় গিয়ে দেখি, একটা মুরগি অনেকগুলো বাচ্চা দিয়েছে। আমি ওদের নিয়ে মাতোয়ারা হয়ে গেলাম এবং ওদের ছেড়ে আসতে চাচ্ছিলাম না। বায়না ধরলাম, আমারও ওগুলো লাগবে। মা তো মহা–মুসিবতে পড়লেন। আমি কিছুতেই ওদের পিছ ছাড়ি না। মা আমাকে একরকম জোর করে নিয়ে এলেন।
 আমি কাঁদতে কাঁদতে ও-বাসা থেকে চলে এলাম। বাসায় আসার পর বিকেলে দেখি আপন দাদি (বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব) মুরগি আর মুরগির বাচ্চাগুলো আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওই বাসায় আমি আপন দাদির অনেক ভক্ত ছিলাম। উনি আমাকে সবকিছুতে প্রশ্রয় দিতেন। আমার নিজের দাদিকে বাদ দিয়ে তাঁকেই ‘আপন দাদি’ বলে ডাকতাম। এই ছিল আমাদের মধুর সম্পর্ক।
আমি কাঁদতে কাঁদতে ও-বাসা থেকে চলে এলাম। বাসায় আসার পর বিকেলে দেখি আপন দাদি (বেগম ফজিলাতুন্নেছা মুজিব) মুরগি আর মুরগির বাচ্চাগুলো আমাকে পাঠিয়ে দিয়েছেন। ওই বাসায় আমি আপন দাদির অনেক ভক্ত ছিলাম। উনি আমাকে সবকিছুতে প্রশ্রয় দিতেন। আমার নিজের দাদিকে বাদ দিয়ে তাঁকেই ‘আপন দাদি’ বলে ডাকতাম। এই ছিল আমাদের মধুর সম্পর্ক।
আরেকজনের আমি খুব ভক্ত ছিলাম, যিনি হচ্ছেন হাসুমণি (জননেত্রী ও মাননীয় প্রধানমন্ত্রী, শেখ হাসিনা)। তিনি আমার মায়ের শুধু মামাতো বোনই ছিলেন না, মায়ের বান্ধবীও ছিলেন। তাই হাসুমণির কোলে জয়কে (সজীব ওয়াজেদ জয়, প্রধানমন্ত্রীর উপদেষ্টামণ্ডলীর সদস্য) দেখলে আমি অভিযোগের সুরে জিজ্ঞেস করতাম, ‘হাসুমণির কোলে জয় কেন?’
হাসুমণির যেই গুনটা আমার সবচেয়ে বেশি ভালো লাগত, তা হচ্ছে তাঁর মমত্ববোধ। প্রান্তিক মানুষের প্রতি তাঁর বিশেষ সমবেদনা ছিল। শিশুদের থেকে শুরু করে গৃহকর্মীদের প্রতি, এমনকি পশুপাখি ও জীবজন্তুর প্রতিও হাসুমণির প্রচণ্ড মায়া ছিল। এই মানবিক বৈশিষ্ট্যের বিবেচনায় তিনি সবার থেকে আলাদা। তিনি আমাদের বাচ্চাদের সাথে অত্যন্ত সদয় ছিলেন। বাচ্চাদের তিনি অনেক সময় দিতেন, এবং সত্যিকার অর্থে যত্নশীল ছিলেন শিশুদের মত ও মতামতের প্রতি।
একবার আমরা দিল্লি গেলাম। দাদি-নানি (আমার দাদি আর নানি দুই বোন), রেখা ফুফু আর আমরা দুই ভাই। হাসুমণি, রেহানা ফুফু আমাদের পেয়ে প্রচণ্ড আদর-যত্ন করলেন। তাঁরা মনে হয় আমাদের পেয়ে তাঁদের নিজ শোক সংবরণ করার শক্তি পেলেন। আমার সব দুষ্টামি তাঁরা মেনে নিতেন। জয় অনেক ঠান্ডা প্রকৃতির এবং সৃষ্টিশীল ছিল। সারাক্ষণ প্লেডো দিয়ে বিভিন্ন জিনিস বানাত। ওর ধৈর্য দেখে আমি অস্থির হয়ে যেতাম। আমি ওর সাথে দৌড়াদৌড়ি বা ছোঁয়া-ছুঁয়ি খেলতে চাইতাম। কিন্তু ওর ওসব খেলার প্রতি কোনো আগ্রহ ছিল না। অনেক শৃঙ্খলার সাথে জীবনযাপন করত। আমি অস্থির হয়ে ওর তৈরি করা সবকিছু ভেঙে দিতাম। ও রাগ করে আমার পিছে দৌড়াত, এতে আমার উদ্দেশ্যও হাসিল হতো। আমি পালাতাম। দাদি আর নানি আমাদের গোলমাল ঠেকাতে এসে মাঝেমধ্যে ব্যথাও পেতেন।
জয় সেটাতে অনেক বিচলিত হয়ে আমার নানিকে বলত, ‘আপনে কেন মাঝখানে এসে ব্যথা পেলেন?’ দাদিকে দেখিয়ে বলত, ‘উনি তো ঠেকাতে আসে না!’ হাসুমণি রেহানা ফুফু কিছুই বলত না। আমাদের এসব কার্যকলাপ দেখে মনে হয় মজা পেতেন। তাঁদের অনেক ধৈর্যশক্তি।
এভাবে প্রায় বছর তিনেক হয়ে গেল। আমিও অভ্যস্ত হয়ে গেলাম বাবা-মা ছাড়া জীবনে। এর মধ্যে বাংলাদেশে ফিরে আসার ব্যবস্থা নেওয়া হলো। আবার সীমানা পেরিয়ে ফিরে আসা। আমাদের বাঙ্গরের প্রতিবেশীরা অনেক মন খারাপ করল। ওদের সাথে আমাদের খুব আন্তরিকতা হয়ে গিয়েছিল, পরিবারের মতো। ঠিক হলো আমি, তাপস, রেখা ফুফু, দাদি আগে ফিরব। পরে চাচারা আসবে। ফিরে আসতে আসল কষ্টটা ছিল কঠোর বাস্তবতার অনুধাবন যে, বাবা-মা আসলে লন্ডনেও নাই; তাঁরা আকাশে হারিয়ে গেছে অজস্র তারার মাঝে। এই বাস্তবতায় মন মানতে না চাইলেও আমাদের কোনো কিছু করার ছিল না। কাকে কী বলব? কেউ তো ভালো নেই। খামাখা সবাইকে এ ব্যাপারে বিরক্ত করে লাভ কী? তাঁরা তো বাবা-মাকে ফিরিয়ে দিতে পারবেন না, পারলে তো আগেই দিতেন।
আমার মা গান গাইতে অনেক ভালোবাসতেন। আমাদের ঘুম পাড়ানোর সময় গাইতেন আঞ্জুমান আরা বেগমের সেই বিখ্যাত ঘুমপাড়ানি গান—‘খোকন সোনা বলি শোন/থাকবে না আর দুঃখ কোনো/মানুষ যদি হতে পারো।/এই কথাটি মনে রেখ/দুঃখীজনের সহায় থেকো।’ আমরা দুই ভাই বিভিন্ন প্রতিকূলতার মধ্যে মানুষ হওয়ার সেই নিরন্তর চেষ্টা চালিয়ে যাচ্ছি। যেন ঘুমপাড়ানি এই গানের মধ্য দিয়ে, মা জীবনের সকল উপদেশ দিয়ে গেছেন। শুধু আফসোস মা দেখতে পারলেন না! দেখতে পারলেন না যে, আমরা পড়াশোনা শিখে তাঁর আশা-আকাঙ্ক্ষার প্রতিফলন ঘটানোর চেষ্টা করেছি।
মায়ের লেখাপড়ার প্রতি অনেক ঝোঁক ছিল। তাঁর মৃত্যুর পর তাঁর এমএ পরীক্ষার ফল বের হয়। তিনি রাষ্ট্রবিজ্ঞানে এমএ পাস করেছিলেন।
আগস্ট মাস এলে মানুষ জানতে চায়, বাবা-মা হারা আমাদের ছোটবেলা কীভাবে কেটেছে। কেমন ছিল আমাদের বেড়ে ওঠা? তাঁদের জন্যই আমার এই লেখা। অবশ্যই আমাদের বেড়ে ওঠা আর দশটা বাচ্চার মতো ছিল না। অত্যন্ত কোমল বয়সেই আমরা রাজনৈতিক প্রতিহিংসা আর রাজনৈতিক হত্যাকাণ্ডের শিকার। আমি এও জানি, নির্বাসিত শিশু হিসেবে আমাদের অভিজ্ঞতা এক আকর্ষণীয় একাডেমিক আলোচনা হিসেবে জায়গা পেতে পারে। তবুও বলব, তুলনামূলকভাবে অনেক এতিম বাচ্চার তুলনায় আমাদের শৈশব কেটেছে পরিবার-পরিজনের মায়া-মমতায়। আমার আত্মীয়-স্বজনদের আমাদের প্রতি মমত্ববোধ আর ভালোবাসার কোনো কমতি ছিল না। বরং আমরা একদিক দিয়ে ভাগ্যবান যে, বাবা-মায়ের ভালোবাসায় বঞ্চিত হলেও অন্য স্বজনদের স্নেহ-মমতা আমরা অনেক বেশিই পেয়েছি। যেটা কেউই পায় না। তবে এত আদর-যত্ন, ভালোবাসার মধ্যেও আমি অবশ্যই বাবা-মাকে খুঁজেছি।
মায়ের গাওয়া নির্মলা মিশ্রার আরেকটি গানের কথা মনে হয়—‘ও তোতা পাখীরে/শিকল খুলে উড়িয়ে দিব/আমার মাকে যদি এনে দাও/… ঘুমিয়ে ছিলাম মায়ের কোলে,/কখন যে মা গেল চলে? সবাই বলে ওই আকাশে/লুকিয়ে আছে খুঁজে নাও।’ যতই অনুভূতি রুদ্ধ করে রাখি, যতই খেলাধুলায় মেতে থাকি, শিশুরা যে মা-বাবাকে খুঁজে বেড়াবে—এটাই প্রকৃতির রীতি।
[বি. দ্র. : এই লেখা সম্পূর্ণরূপে আমার শিশুকালের স্মরণশক্তির ওপর ভিত্তি করে লেখা। তাই আমি ক্ষমা চেয়ে নিচ্ছি এই মর্মে যে, যদি ভুলবশত কাউকে আমি ভুলে গিয়ে থাকি। এখানে অনেক ঘটনা অসম্পূর্ণ ও আংশিক সত্য হতে পারে। কারণ, অপরিপক্ব এক ছয় বছরের শিশুর খণ্ড খণ্ড স্মৃতির ওপর এই কাহিনি গাথা। তাই পরিপূর্ণ সত্যতার কোনো দাবি এখানে আমি করছি না। ]
শেখ ফজলে শামস পরশ: ১৯৭৫ সালের ১৫ আগস্ট শহীদ শেখ ফজলুল হক মণি ও আরজু মণির বড় ছেলে। চেয়ারম্যান, বাংলাদেশ আওয়ামী যুবলীগ
সর্বশেষ খবর পেতে Google News ফিড ফলো করুন
সম্পর্কিত

নজিরবিহীন বাস্তবতায় একটি সরকার
দলীয় রাজনৈতিক সরকারের সঙ্গে একটি অন্তর্বর্তী সরকারের তুলনা হতে পারে কি না, সেই প্রশ্ন পাশে রেখেই ইউনূস সরকারের কাজের মূল্যায়ন হচ্ছে এর ১০০ দিন পেরিয়ে যাওয়ার সময়টায়। তবে সাধারণ মানুষ মনে হয় প্রতিদিনই তার জীবনে সরকারের ভূমিকা বিচার করে দেখছে।
১৬ ঘণ্টা আগে
অস্থিরতার লক্ষণ অস্পষ্ট নয়
শেখ হাসিনা সরকারের পতনের ১০০ দিন পার হয়ে গেছে। ১০০ দিনে অন্তর্বর্তী সরকারের সাফল্য-ব্যর্থতা নিয়ে আলোচনা-সমালোচনা কিছু যে হয়নি, তা নয়। তবে দেশ পরিচালনার দায়িত্বে যাঁরা আছেন, তাঁদের মধ্যে অস্থিরতার লক্ষণ অস্পষ্ট নয়। এর মধ্যেই তিন দফায় উপদেষ্টার সংখ্যা বাড়ানো হয়েছে।
১৬ ঘণ্টা আগে
খোলনলচে
বাংলা ভাষায় অতিপরিচিত একটি শব্দবন্ধ হলো ‘খোলনলচে’। যাপিত জীবনে কমবেশি আমরা সবাই শব্দবন্ধটি প্রয়োগ করেছি। বাংলা বাগধারায় আমরা পড়েছি ‘খোলনলচে পালটানো’। বাংলা অভিধানে খোল শব্দের একাধিক অর্থ রয়েছে।
১৬ ঘণ্টা আগে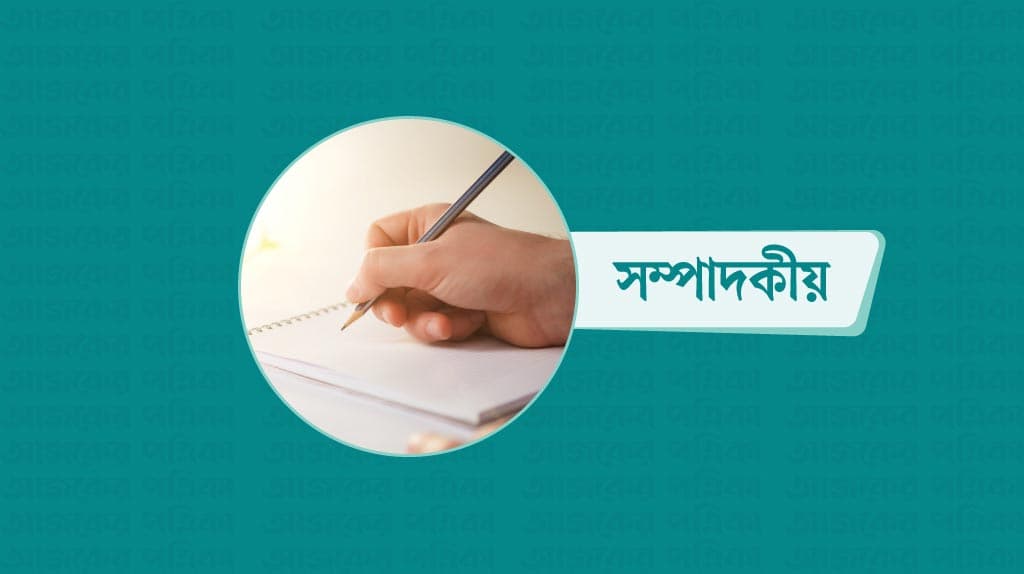
সাবলেট প্রতারণা
অফিসে যাতায়াতের সময় স্টাফ বাসে পরিচয়ের সূত্রে ফারজানা আক্তার আজিমপুরে নিজের বাসায় সাবলেট দিয়েছিলেন ফাতেমা আক্তার শাপলা নামের এক নারীকে। কিন্তু ফাতেমা যে একটি প্রতারক চক্রের সদস্য, সেটা তাঁর জানা ছিল না।
১৬ ঘণ্টা আগে



